
১৯৪৭ সালে দেশ ভাগ ও ১৯৫২ সালের ভাষা-আন্দোলন এ-ভূখণ্ডের জনজীবনকে প্রবলভাবে আলোড়িত করেছে। একুশের অভিঘাত ও রক্তাক্ত অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের গল্পকারদের সবচেয়ে বেশি জীবনমুখী করেছে, মানবিক বোধে উজ্জীবিত করেছে। স্বতঃস্ফূর্তভাবেই তারা লিখেছেন রক্ত ও অশ্রুপাতের গল্প। যুগের বেদনা ও যন্ত্রণাকে ধারণ করেছে একুশের ছোটগল্প।
ভাষা-আন্দোলনের প্রত্যক্ষ স্বাক্ষর নিয়ে ১৯৫৩ সালে প্রকাশিত হয়েছিল হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত একুশে ফেব্রুয়ারি সংকলন। গল্প, কবিতা, গান, ছড়া ও একুশের স্মৃতিচারণ গ্রন্থিত হয়েছিল এই সংকলনে। এই মহত্তম সংকলনে কয়েকটি কবিতা অসাধারণ জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। তবে ভাষা-আন্দোলন নিয়ে লেখা গল্পের যদি হিসাব নেয়া হয় তাহলে প্রথমেই মনে পড়বে, একুশে ফেব্রুয়ারি সংকলনের কথা। এই সংকলনে পাঁচটি গল্প অন্তর্ভুক্ত হয়। এগুলো হচ্ছে: ‘মৌন নয়’- শওকত ওসমান, ‘হাসি’- সাইয়িদ আতীকুল্লাহ, ‘দৃষ্টি’- আনিসুজ্জামান, ‘অগ্নিবাক’- আতোয়ার রহমান, ‘বহ্নি’- সিরাজুল ইসলাম।
পরবর্তীকালে বাংলা একাডেমি থেকে রশীদ হায়দার সম্পাদিত একুশের গল্প (১৯৮৪) নামে একটি সংকলন প্রকাশিত হয়। এই সংকলনে সিরাজুল ইসলামের গল্পটি ছাড়া একুশের প্রথম সংকলনের বাকি চারটি গল্পসহ আরও আটটি গল্প অন্তর্ভুক্ত হয়। রশীদ হায়দার সম্পাদিত একুশের গল্পের অন্য গল্পগুলো হচ্ছে: ‘খরস্রোত’- সরদার জয়েনউদ্দীন, ‘আমরা ফুল দিতে যাবো’- মিরজা আবদুল হাই, ‘প্রথম বধ্যভূমি’- রাবেয়া খাতুন, ‘বরকত যখন জানতো না সে শহীদ হবে’- বশীর আল হেলাল, ‘ছেঁড়া তার’- মাহমুদুল হক, ‘মীর আজিমের দুর্দিন’- সেলিনা হোসেন, ‘উনিশ শ তিয়াত্তরের একটি সকাল’- আহমদ বশীর, ‘চেতনার চোখ’- আনিস চৌধুরী। এই পরিসংখ্যানের বাইরেও হয়তো একুশের কিছু উল্লেখযোগ্য গল্প রয়ে গেছে। তবে এর সংখ্যা খুব বেশি বলে মনে হয় না। আমরা আশা করব কেউ না কেউ একুশভিত্তিক একটি পূর্ণাঙ্গ গল্প-সংকলন সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে আসবেন।
‘মৌন নয়’ শওকত ওসমানের গল্প। ভাষা-আন্দোলনে ছেলেহারা এক বৃদ্ধের শোকবিহ্বলতার গল্প। চলন্ত একটি বাস, বাসের যাত্রী ছাত্র, চাষি, কেরানি, ড্রাইভার, কন্ডাক্টর সবাই যেন মুখের ভাষা হারিয়ে ফেলেছে। বাসের হেলপার, যে কিনা প্রতিদিন অসংখ্য স্থানের নাম উচ্চারণ করে ডাকতো ভাড়া চেয়ে চেয়ে, দ্রুত হাতে ভাঙতি পয়সা গুনে দিতে দিতে বাসের তালে হেলেদুলে ভারসাম্য রক্ষা করে পুরো বাসে আনাগোনা করতো প্রচণ্ড ভিড় ঠেলে, সেও নির্বিকার, ভাষাহীন। বিমূঢ় বিষাদে সবাই স্তব্ধ। বাস চলছে কিন্তু গন্তব্য জানা নেই। নির্বিকার যাত্রীদল বসে আছে, কারো কোনো উদ্বেগ নেই, তাড়াহুড়া নেই বাড়ি ফেরার।
সমস্ত নীরবতাকে টুকরো টুকরো করে হঠাৎ সেই বৃদ্ধ আর্তনাদ করে উঠল। চোখের দৃষ্টি অপলক, বৃদ্ধ এইবার ডুকরে আর্তনাদ করে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে চুরমার হয়ে গেল নীরবতার জগদ্দল- ‘কী দোষ করেছিল আমার ছেলে? ওরা কেন তাকে গুলি করে মারল? কী দোষ, কী দোষ করেছিল সে? উঃ’
‘কী দোষ করেছিল সে?’- এই জিজ্ঞাসাচিহ্ন ভাসছে তার চোখের ওপর। এখনই মুখ থুবড়ে পড়বে বৃদ্ধ বাসের মেঝেয়।
সমস্ত যাত্রী তখন নিজের জায়গা ছেড়ে বৃদ্ধের ওপর ঝুঁকে পড়েছে। চাষি দুজন তার কোমর জড়িয়ে ধরল, যেন পড়ে না যান। ড্রাইভারের এক হাতে স্টিয়ারিং, অন্য হাত সে সবার আগেই বৃদ্ধের দিকে এগিয়ে দিয়েছে। জোড়া জোড়া জ্বলন্ত চোখের দৃষ্টি স্ফুলিঙ্গ ঠিকরে পড়ে। দমকে দমকে সিংহ-গর্জন এখনই ফেটে পড়বে।
‘খরস্রোত’ সরদার জয়েনউদ্দীনের গল্প। ১৯৫৩ সালে লেখা এ-গল্পটি শোকের বিশাল বেদনা ধরে রেখেছে। এ হচ্ছে বরকতের মায়ের কান্না। ১৯৫২ সালের এক সকালে বরকত তার মাকে বলেছিল: মা তোমাকে মা বলে যে ডাকবো তা নাকি আর পারবো, না। বলতো মা আমরা কি তা মেনে নিতে পারি? আজ তাই আমরা তার জন্য শান্তিযুদ্ধ করবো। আমরা ধর্মঘট করবো। তুমি আশীর্বাদ করো। মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে আনন্দে সে বেরিয়ে যায়, কিন্তু আর ফিরে আসেনি। বরকতের মা এসব বলে বলে কাঁদে, সারা বছর কাঁদে।
মিরজা আবদুল হাইয়ের গল্প ‘আমরা ফুল দিতে যাবো’-তে বায়ান্নর ভাষা-আন্দোলনকে ভিন্ন একটি দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার প্রয়াস রয়েছে। পাকিস্তান সরকারের অধীনে চাকরি করলেও সিভিলিয়ানদের মধ্যে অনেকে স্বদেশপ্রেমী হওয়ার কারণে শাসকগোষ্ঠীর রুদ্রদৃষ্টিতে পড়েছিলেন। সমগ্র জাতির চেতনা যে বিষয়কে কেন্দ্র করে একদিন জাগ্রত হয়েছিল, সে বিষয়কেই এ গল্পে উপজীব্য করা হয়েছে। রাষ্ট্রভাষার আন্দোলনে সমসাময়িক ছাত্রসমাজ কীভাবে কতটা সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছিল তার প্রমাণ এ গল্পটিতে পাওয়া যায়।
আনিস বিজ্ঞানের ছাত্র ছিল। কিন্তু মাতৃভাষার প্রশ্নে তার বড় পরিচয় ছিল সে একজন সচেতন ছাত্র। বায়ান্ন সালের পরবর্তী সময়েও ভাষা আন্দোলন এদেশের মানুষের মনে কত সজীব ছিল তা আমরা এ গল্পে দেখতে পাই। (মোহাম্মদ জাহিদ হোসেন, বাংলাদেশের ছোটগল্প: জীবন ও সমাজ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃষ্ঠা ১৪১)।
নূরউল আলমের ‘একালের রূপকথা’ গল্পের পটভূমিও বায়ান্নর একুশের ফেব্রুয়ারি। এ গল্পের হামিদ সাহেব উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা। তার ছেলে কাসেম পড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে। পিতার নিষেধকে উপেক্ষা করে কাসেম নিজের বিবেকের তাড়নায় যোগ দেয় ভাষা-আন্দোলনে। হামিদ সাহেব ছেলের অবাধ্যতায় ক্ষুব্ধ হয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে গেলেন। যেতে যেতে তিনি দেখলেন রাস্তায় রাস্তায় পুলিশ, সশস্ত্র প্রহরায় দাঁড়িয়ে আছে। এরমধ্যে ছাত্রদের স্লোগান ‘রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই’। গল্পের এ বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করতে গিয়ে এদেশের ছাত্ররা কতটা জুলুম-নির্যাতন সহ্য করেছে। দিতে হয়েছে কত রক্ত। উত্তর-প্রজন্ম কি ভুলে যাবে এই আত্মত্যাগের কথা?
‘সিঁড়ি’ গল্পে সাঈদ-উর রহমান তুলে ধরেছেন গ্রামের এক বৃদ্ধ করিমের কথা। তার ছেলে সিরাজ ভাষা আন্দোলনে বন্দি হয়ে জেলে আছে। বৃদ্ধ করিম ছেলেকে দেখতে নৌকা করে ঢাকায় যাবেন। কারণ, ছেলে সিরাজের আজ মুক্তি পাওয়ার কথা; কিন্তু বউমা মরিয়মের ভাত রান্না হতে দেরি হচ্ছে। ১৯৫২-র পরে অবশ্যই কিছু সাড়া জেগেছিল। কিন্তু প্রাণের সেই জোয়ার আমাদের সাহিত্যের দু-কূলকে প্লাবিত করার আগেই তাতে ভাটা পড়েছিল। কথাটি হয়তো মিথ্যা নয়। এবং সেটা আমাদের ভয়ঙ্কর দুর্ভাগ্যের কথা। কিন্তু তবু সেই ১৯৫২-ই হচ্ছে ল্যান্ডমার্ক। আমাদের সাফল্যের জয়যাত্রা ওখান থেকেই শুরু হয়েছিল।
আমাদের ধারণা সে যাত্রার ইতি হয়নি, নানা কারণে মাঝপথে থেমে আছে মাত্র। উৎসের কাছে একটি নদীর অগ্রযাত্রা একটি প্রস্তরখণ্ডেই ব্যাহত হতে পারে। কিন্তু অবধারিত নববর্ষায় সে প্রস্তরখণ্ড ভেসে যাবেই। আমাদের সাহিত্যের ভাগ্যে যাই ঘটে থাকুক না কেন, ওই ১৯৫২-র উৎস মিথ্যা নয়। মিথ্যা নয় আমাদের পঞ্চাশের দশক।’ (বশীর আল হেলাল, ‘বাংলাদেশের ছোটগল্প’, উত্তরাধিকার, শহীদ দিবস সংখ্যা, ১৯৭৪, পৃষ্ঠা ৩০৫)
একুশের চেতনার পরিপাটি বিস্তার আমাদের ছোটগল্পে খুবই প্রত্যক্ষ এবং বাস্তব। যদিও সৃষ্টির পরিসংখ্যান খুব দীর্ঘ নয়, তবু শুধু যুগের দাবিকে ধারণ করার জন্য একুশের ছোটগল্পের মূল্য ও মর্যাদা অপরিসীম। আমাদের ইতিহাসের রক্তাক্ত অধ্যায়ের এক বহুবিচিত্র অ্যালবাম একুশের ছোটগল্প।
মানবকণ্ঠ/এফআই
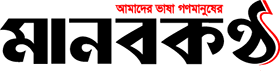





Comments