
জামায়াতে ইসলামী দলটি সূচনালগ্ন থেকেই একটা মোটাবুদ্ধি ও আবেগের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। তারপরও তাদের গণতান্ত্রিক ধারায় টিকে থাকতে যে সকল বিশেষ কৌশল ও বুদ্ধির প্রয়োগ দেখা যায় তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে। পর্যায়ক্রমে সুশৃঙ্খলতার সাথে তাদের কাঠামোগতভাবে গড়ে উঠা, দলে জ্ঞান চর্চার ধারাবাহিকতা বজায় রাখা, চেইন অব কমান্ড মেনে চলা, ঊর্ধ্বতনদের চূড়ান্ত রায়কে অম্লান বদনে মেনে নেয়া, ফান্ড গঠনে বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করা, এসবই অন্য রাজনৈতিক দলগুলো থেকে স্বতন্ত্র।
তা সত্ত্বেও তারা রাজনীতিতে বরাবরই নিজেদেরকে মেলে ধরে গণতান্ত্রিকভাবে সফল হতে ব্যর্থ হচ্ছে কেনো? এর নেপথ্যের কারণগুলো তাদের ভালো মত খতিয়ে দেখা উচিত। নচেৎ ২০২৬ সালের জাতীয় নির্বাচনেও তাদের ভরাডুবি না হলেও মাঝারি অবস্থার চেয়ে ভালো কিছু হবে বলে মনে হয় না। তাই আমি মনে করি, তাদেরকে এখনই সচেতন হওয়ার উপযুক্ত সময়, যদিও অতীতের ভুলগুলো শুধরে নিয়ে আর সামনে এগিয়ে পুরোপুরি সফলতা অর্জন সম্ভব নয়। তবুও আমার ক্ষুদ্র চিন্তা থেকে কিছু সমালোচনা করতে বাধ্য হচ্ছি।
এ দলটি ১৯৪১ সালের ২৬ আগস্টে মাওলানা মওদুদির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হলেও তা ছিল কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মত দূরদর্শী ষড়যন্ত্রেরই একটা অংশ বিশেষ। কংগ্রেসের জন্ম ১৮৮৫ সালের ২৮ ডিসেম্বর বোম্বাইয়ের গোকুলদাস তেজপাল সংস্কৃত কলেজে। অ্যালান অক্টাভিয়ান হিউমকে কংগ্রেসের প্রধান প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে ধরা হয়।
তবে এর সঙ্গে অনেক ভারতীয় নেতাও যুক্ত ছিলেন, যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন দাদাভাই নওরোজি, ফিরোজ শাহ মেহতা, বদরুদ্দিন তৈয়বজী, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। ১৮৮৫ সালের ২৮ ডিসেম্বর বোম্বেতে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ৭২ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। প্রথম অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। মূলতঃ এদিন থেকেই ইংরেজরা হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপনের সূত্রপাত ঘটায়।
অনুরূপ মুসলিম লীগের বিষয়টিও। বঙ্গভঙ্গ এবং মুসলিম লীগ গঠন দুটি পৃথক ঘটনা হলেও, একটি অন্যটির সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। মূলতঃ ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ মুসলিম লীগ গঠনের পটভূমি তৈরি করেছিল যেখানে ১৯০৫ সালে ব্রিটিশ ভারতের ভাইসরয় লর্ড কার্জন বাংলা প্রদেশকে দুটি ভাগে বিভক্ত করার সিদ্ধান্ত নেন। আর এটিই বঙ্গভঙ্গ নামে পরিচিত।
কারণ ব্রিটিশ সরকারের যুক্তি ছিল, অবিভক্ত বাংলা প্রদেশের বিশাল আয়তন (প্রায় ১,৮৯,০০০ বর্গ মাইল) এবং ৭ কোটি ৮০ লাখের বেশি জনসংখ্যা নিয়ে প্রশাসনিক কাজ পরিচালনা করা কঠিন। তারা পূর্ববঙ্গের অনুন্নত অঞ্চলগুলোর উন্নয়নের জন্য একটি নতুন প্রদেশ গঠনের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন।
তবে সমালোচকদের মতে, এর আসল উদ্দেশ্য ছিল ‘উরারফব ধহফ জঁষব’ বা বিভাজন ও শাসন নীতি প্রয়োগ করে বাঙালি হিন্দুদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে দুর্বল করা। বঙ্গভঙ্গের ফলে গঠিত হয় দুটি প্রদেশ: পূর্ববঙ্গ ও আসাম: ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী বিভাগ এবং আসাম নিয়ে গঠিত হয় নতুন এই প্রদেশ, যার রাজধানী ছিল ঢাকা। এখানে মুসলিম জনগোষ্ঠী ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ।
পশ্চিমবঙ্গ: পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে গঠিত হয় এই প্রদেশ, যার রাজধানী ছিল কলকাতা। এখানে হিন্দুরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। উল্লেখ্য, হিন্দু বাঙালিরা বঙ্গভঙ্গের তীব্র বিরোধিতা করে। তারা একে বাঙালি জাতির ঐক্য নষ্ট করার ব্রিটিশ ষড়যন্ত্র হিসেবে দেখে। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তীব্র আন্দোলন গড়ে ওঠে, যা স্বদেশী আন্দোলন নামে পরিচিত। এই আন্দোলনের ফলে ব্রিটিশ পণ্য বর্জন করে দেশীয় শিল্পের প্রসারে জোর দেয়া হয়। এদিকে মুসলিমরা বঙ্গভঙ্গকে স্বাগত জানায়।
তারা মনে করত, নতুন প্রদেশে তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা বাড়বে। ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ-সহ অনেক মুসলিম নেতা বঙ্গভঙ্গের পক্ষে ছিলেন। ১৯০৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত ‘মোহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্স’-এর বার্ষিক সম্মেলন শেষে ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহর প্রস্তাবে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ (অষষ ওহফরধ গঁংষরস খবধমঁব) গঠিত হয়। মুসলিম লীগের প্রথম সভাপতি স্যার সুলতান মুহাম্মদ শাহ, যিনি তৃতীয় আগা খান (অমধ কযধহ ওওও) হিসেবেও পরিচিত, মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠায় তার ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আগা খান হলো শিয়া ইসলামের ইসমাইলি শাখার নিজারি সম্প্রদায়ের ইমামদের একটি বংশগত উপাধি।
তিনি ছিলেন এই সম্প্রদায়ের ৪৮তম ইমাম। মূলতঃ তিনি ১৮৭৭ সালের ২ নভেম্বর ব্রিটিশ ভারতের করাচিতে জন্মগ্রহণ করেন। তার পূর্বপুরুষদের ধারা হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বংশের সাথে সম্পর্কিত বলে বিশ্বাস করা হয়। আগা খান ইউরোপে তার শিক্ষা সম্পন্ন করেন, যেখানে তিনি ইটন কলেজ এবং কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছিলেন। তিনি একজন সফল ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার মালিক এবং প্রজননকারী হিসেবেও পরিচিত ছিলেন।
উল্লেখ্য, তিনি এই পদটি ১৯১২ সাল পর্যন্ত অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পালন করেন। এর আগে, ১৯০৬ সালের ১ অক্টোবর তিনি ভাইসরয় লর্ড মিন্টোর কাছে মুসলিমদের একটি প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, যা সিমলা ডেপুটেশন নামে পরিচিত। এই ডেপুটেশনে তিনি মুসলিমদের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচন ব্যবস্থার দাবি জানিয়েছিলেন। আর এই ঘটনাটা মুসলিম লীগ গঠনের পথ প্রশস্ত করেছিল। এবার আসা যাক তৃতীয় রাজনৈতিক দল গঠনের প্রসঙ্গে।
কৃষক প্রজাপার্টি ছিল ব্রিটিশ ভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দল, যা মূলত বাংলার কৃষক ও সাধারণ জনগণের স্বার্থ রক্ষার জন্য গঠিত হয়েছিল। এটি শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক-এর নেতৃত্বে পরিচালিত হয় এবং বাংলার রাজনীতিতে একটি নতুন ধারা তৈরি করে। উল্লেখ্য, উনিশ শতকে বাংলার কৃষকরা জমিদার ও মহাজনদের শোষণ-নির্যাতনের শিকার হতো।
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদাররা জমির নিরঙ্কুশ মালিকানা পেলেও কৃষকদের অবস্থা শোচনীয় ছিল। এই পরিস্থিতিতে কৃষকদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন প্রজা আন্দোলন গড়ে ওঠে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯২৯ সালে নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয় যার নেপথ্যের কারণে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী ১৯৩৭ সালে প্রাদেশিক নির্বাচনের ঘোষণা হলে, এ. কে. ফজলুল হক নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি থেকে বেরিয়ে এসে ১৯৩৬ সালে কৃষক প্রজাপার্টি নামে একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দল গঠন করেন। এই দলের মূল লক্ষ্য ছিল কৃষকদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।
কৃষক প্রজাপার্টির মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলো তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে স্পষ্ট করা হয়েছিল: ১) জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ: বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি প্রথা বিলোপ করে কৃষকদের জমির মালিকানা প্রদান। ২) ঋণ মওকুফ: মহাজনদের ঋণের জাল থেকে কৃষকদের মুক্ত করা এবং তাদের ঋণ মওকুফ করা। ৩) শিক্ষার প্রসার: অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন। ৪) খাজনা হ্রাস: কৃষকদের উপর থেকে অতিরিক্ত খাজনার বোঝা কমানো।
৫) কৃষি ঋণ: সহজ শর্তে ও সুদমুক্ত কৃষি ঋণের ব্যবস্থা করা। মজার ব্যাপার হলো, ১৯৩৭ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে কৃষক প্রজাপার্টি মুসলিম লীগ এবং কংগ্রেসের মতো বড় দলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। ফলে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস: ৫৪টি আসন, স্বতন্ত্র মুসলিম: ৪২টি আসন, নিখিল ভারত মুসলিম লীগ: ৪০টি আসন, কৃষক প্রজাপার্টি: ৩৫টি আসন পায়। এখানে দেখা যায় যে, কংগ্রেস একক বৃহত্তম দল হলেও, স্বতন্ত্র মুসলিম প্রার্থীরা এবং মুসলিম লীগ ও কৃষক প্রজাপার্টি মিলে মুসলিমদের জন্য সংরক্ষিত ১১৭টি আসনের বেশিরভাগ পায়।
বিশেষ করে স্বতন্ত্র মুসলিম প্রার্থীরা একটি বড় শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়, যা কোনো একক দলের পক্ষে সরকার গঠন করা অসম্ভব করে তোলে। ফলে স্বতন্ত্র মুসলিম দলটির ৪২টি আসনে বিজয় লাভ জামায়াত ইসলামী দলটি গঠনে স্বপ্ন বুননে সহায়তা করে। নির্বাচনের পর, এ. কে. ফজলুল হক স্বতন্ত্র মুসলিম প্রার্থীদের সমর্থনে মুসলিম লীগের সাথে মিলে কোয়ালিশন সরকার গঠন করেন এবং বাংলার প্রথম প্রধানমন্ত্রী হন। এই সময় তিনি ঋণ সালিশি বোর্ড গঠন করেন, যা কৃষকদের ঋণের বোঝা কমাতে সাহায্য করে। তবে মুসলিম লীগের সাথে মতপার্থক্যের কারণে ১৯৪১ সালে তার সরকারের পতন ঘটে। পরে তিনি কংগ্রেসের সাথে মিলে নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করেন। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে কৃষক প্রজাপার্টি কৃষক শ্রমিক পার্টি নামে পরিচিতি লাভ করে এবং ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
এবার আসা যাক জামায়াত ইসলামী দলটির প্রসঙ্গে। মূলতঃ জামায়াত ইসলামী নামমাত্রে একটি ইসলামী রাজনৈতিক দল, যা ১৯৪১ সালের ২৬ আগস্ট ব্রিটিশ ভারতের লাহোরে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ইসলামী চিন্তাবিদ ও দার্শনিক সাইয়েদ আবুল আ’লা মওদুদী। ১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বরে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বক্তৃতায় মওদুদী মুসলিম লীগের সাথে তার মতপার্থক্য তুলে ধরেন। এরপর ১৯৪১ সালের ২৫ ও ২৬ আগস্ট লাহোরের ইসলামিয়া পার্কে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে রাজনৈতিক দল হিসেবে জামায়াতে ইসলামী হিন্দ আত্মপ্রকাশ করে এবং মাওলানা মওদুদী দলটির প্রথম আমির (সভাপতি) নির্বাচিত হন।
এতে বুঝা যাচ্ছে, গণতন্ত্রে দল-মত-পথ সৃষ্টি করা হয়, বিভিন্ন ফ্যাতনাকে জিইয়ে রাখার জন্য। প্রয়োজনে তা সৃষ্টি করা হয় এবং প্রয়োজন শেষে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করা হয়। যেমন মুসলিম লীগ আজকে জাদুঘরে চলে গেছে। আওয়ামী লীগ যাওয়ার পথে। এ. কে. ফজলুল হকের কৃষক শ্রমিক পার্টিরও কোনো অস্তিত্ব নেই। মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর ন্যাপ দলটিরও তেমন একটা চিহ্ন নেই বললেই চলে।
কমিউনিস্ট বা সমাজতান্ত্রিক দলগুলোও গ্রহণযোগ্যতা হারিয়েছে অনেক আগেই। আর নতুন ইসলামী দলগুলো তো হালে পানিই পাচ্ছে না। তো জামায়াত ইসলামী দলটি ১৯৭১ সালের বিরোধিতা করে টিকে থাকবে কি করে? ১৯৭৭ সালে প্রতিষ্ঠিত শিবির দলটি যদি ১৯৭১ সালের যুদ্ধাপরাধীদের সাথে সম্পর্ক ছেদ করতে পারতো যা ১৯৮৫ সালে একবার চেষ্টা করেছিল মাত্র এবং ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানের এক বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে ২০২৫ সালের আগস্টে যদি ঢাকার শাহবাগে টিএসসির প্রদর্শনীতে রাজাকারদের ছবি ফলাও করে দৃশ্যায়িত না করতো তথা ৭১ প্রীতি না দেখাতো তাহলে হয়তো একটা আশা ছিল।
অবশ্য এটা শাহবাগীরা যখন ইন্ডিয়ার প্ররোচনায় যুদ্ধ অপরাধীদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করিয়ে দিয়েছিল আওয়ামী লীগ সরকারের উস্কানিতে তখনই রাজাকারদের সাথে সম্পর্ক ছেদের বিষয়টি স্পষ্টভাবে বলে দেয়া উচিত ছিল। যদিও এতে কতিপয় জামায়াতের আমিরকে অস্বীকার করা হতো বটে তবে প্রকৃত অর্থে এদেশের সাধারণ জনগণের মন পেতো তারা যারা আজকে ১৯৭১ সালের স্বাধীনতার পক্ষের লোক। আমি অবশ্য বিষয়টি নিয়ে সেই সময়েই লেখালেখি করেছিলাম। কিন্তু কে শোনে কার কথা?
লেখক: গবেষক, রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও দার্শনিক
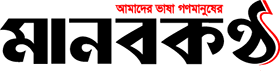





Comments