
‘রাষ্ট্র তখনই কল্যাণমুখী হয়, যখন নেতারা নিজ স্বার্থে নয়, জনগণের সুখে নিজের আনন্দ খুঁজে পান।’- বর্তমান সমাজ ও রাজনীতির প্রেক্ষাপটে জন স্টুয়ার্ট মিল-এর কথাটি খুবই যথার্থ মনে হয়। শুধু মনে হলে ভুল বলা হবে- এটি সমাজ ও রাজনীতির ব্যবস্থার বাস্তবতা। আমাদের সামাজিক বুনিয়াদে ক্রমেই এক বিষাক্ত ছায়া নেমে আসছে। রাজপথ থেকে শুরু করে অলিগলি, শাসনকক্ষ থেকে রাষ্ট্রযন্ত্রের নিচুতলার অফিস- সর্বত্রই এক চরম নৈরাজ্যের অনুভূতি।
হাইজ্যাক, ছিনতাই, চুরি-ডাকাতির মতো সশস্ত্র ও সংঘবদ্ধ অপরাধের উৎকট উপস্থিতি যেন নিত্যদিনের সঙ্গী। অন্যদিকে, নাগরিক সেবা পাওয়ার পথে আমলাতান্ত্রিক জটিলতার দুষ্টচক্রে জনগণ হাবুডুবু খাচ্ছে। এই দুই আপাত-বিপরীতমুখী সংকটের গভীরে গেলে চোখে পড়ে এক অভিন্ন উৎস। রাজনৈতিক নেতাদের সুপরিকল্পিত ভণ্ডামি ও নৈতিক অধঃপতন। এই ভণ্ডামিই অপরাধকে প্রশ্রয় দিচ্ছে, আমলাতন্ত্রকে দুর্নীতিগ্রস্ত করছে এবং সমাজকে এক চরম অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দিচ্ছে।
বাংলাদেশের সমসাময়িক রাজনীতি একটি কঠিন ও দুঃখজনক বাস্তবতার মুখোমুখি। রাজনীতিকে যেখানে হওয়ার কথা ছিল জনসেবা ও ন্যায়ের রক্ষাকবচ, সেখানে তা ক্রমশ হয়ে উঠেছে লোভ, মিথ্যাচার ও স্বার্থসিদ্ধির বাহন। রাজনৈতিক নেতৃত্বের ভণ্ডামি শুধু নৈতিকতার সংকট তৈরি করেনি, বরং সমাজে অপরাধপ্রবণতা, চুরি, ছিনতাই ও হাইজ্যাকের মতো কর্মকাণ্ড বেড়ে যাওয়ার পেছনেও ভূমিকা রেখেছে। ফলস্বরূপ, রাষ্ট্রযন্ত্র আজ নানা ধরনের আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় আচ্ছন্ন, যেখানে সাধারণ মানুষের ন্যায়বিচার ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত।
নেতাদের মুখে উন্নয়নের গীত, শান্তির বুলি আর দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্সের দামি স্লোগান। কিন্তু আড়ালে তাদের কর্মকাণ্ড, কথাবার্তা ও আচরণে ফুটে ওঠে চরম স্ববিরোধিতা ও সুবিধাবাদিতা। বর্তমান সময়ের অনেক রাজনৈতিক নেতা জনগণের সামনে একরকম মুখোশ পরে থাকেন, প্রগতি, দেশপ্রেম ও সেবার বুলি আওড়ালেও নেপথ্যে থাকে ক্ষমতা ধরে রাখার কূটকৌশল, দুর্নীতি ও দলীয় স্বার্থ। এই ভণ্ডামি দীর্ঘমেয়াদে সামাজিক আস্থা বিনষ্ট করে।
মানুষ যখন দেখে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরাই দুর্নীতিতে লিপ্ত, ঘুষের বিনিময়ে সুযোগ-সুবিধা বণ্টন হয়, তখন সাধারণ মানুষের মধ্যেও এক ধরনের নৈতিক অবক্ষয় গড়ে ওঠে। তরুণরা রাজনৈতিক আশ্রয়ে বেড়ে ওঠা অপরাধীদের জীবন দেখে উদ্বুদ্ধ হয় দ্রুত টাকা ও ক্ষমতা অর্জনের পথে। এভাবে রাজনীতির ভণ্ডামি সমাজে অনৈতিকতার ছায়া বিস্তার করে।
এক সময় ছিনতাই, হাইজ্যাক কিংবা সংঘবদ্ধ চুরির ঘটনা কেবল অপ্রতিরোধ্য অপরাধচক্রের সঙ্গে যুক্ত ছিল। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, এই অপরাধগুলোর সঙ্গে রাজনৈতিক পরিচয়ধারী ব্যক্তিরা জড়িত। অনেকে রাজনৈতিক দলের নাম ব্যবহার করে চাঁদাবাজি, দখল, মাদক ব্যবসা কিংবা প্রতারণার মতো অপরাধে যুক্ত। আবার এসব অপরাধীরা প্রশাসনিক বা রাজনৈতিক আশ্রয়ে সহজেই আইনের ফাঁক গলে যায়।
যেমন রাজধানীতে বা বিভাগীয় শহরগুলোতে দেখা যায়, বহু পরিবহন শ্রমিক নেতা, মার্কেট কমিটির সভাপতি বা এলাকাভিত্তিক যুবনেতা সাইনবোর্ডে রাজনৈতিক পরিচয় বহন করলেও বাস্তবে তারা সংঘবদ্ধ চাঁদাবাজি ও ছিনতাইয়ের সঙ্গে যুক্ত। এ ধরনের অপরাধী চক্রের পেছনে রাজনৈতিক শক্তির সুরক্ষা থাকায় তারা ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যায়। ফলস্বরূপ সমাজে অপরাধ প্রবণতা বাড়ে এবং সাধারণ মানুষ সবচেয়ে মারাত্মক ভণ্ডামি হলো সরাসরি অপরাধী সিন্ডিকেট, ছিনতাইকারী চক্র, এমনকি জঙ্গিগোষ্ঠীর সাথে নেতাদের আঁতাত ও লেনদেন।
নির্বাচনী সহিংসতা, প্রতিপক্ষকে দমনে, বা এলাকা দখলে রাখতে নেতারা এসব অপরাধী গোষ্ঠীকে ব্যবহার করেন। বিনিময়ে তারা পায় রাজনৈতিক ছত্রছায়া, মামলা প্রত্যাহার, পুলিশি হয়রানি থেকে মুক্তি, এমনকি ঠিকাদারি বা চাঁদাবাজির লাইসেন্স। এটিই অপরাধীদের সাহস ও শক্তি জোগায়। তারা বুঝে যায়, নেতার আশীর্বাদ পেলে আইন তাদের স্পর্শ করতে পারবে না। ফলে হাইজ্যাক, ছিনতাই হয়ে ওঠে ন্যূনতম ঝুঁকির লাভজনক ব্যবসা। রাজনীতির ভণ্ডামি কেবল সমাজে অপরাধ প্রবণতা বাড়ায় না, প্রশাসনিক স্তরেও তীব্র জটিলতা তৈরি করে। রাজনৈতিক নেতারা প্রশাসনে নিজস্ব লোক বসাতে চায়, ফলে নিয়োগে মেধার চেয়ে দলীয় আনুগত্য গুরুত্ব পায়।
এতে প্রশাসন হয়ে পড়ে অদক্ষ, পক্ষপাতদুষ্ট এবং দুর্নীতিগ্রস্ত। আমলারা রাজনৈতিক ইশারায় চলতে বাধ্য হন। তাই তারা আইন নয়, নেতার কথাকে বেশি গুরুত্ব দেন। এতে প্রশাসন হারায় নিরপেক্ষতা, ফলে জবাবদিহি ব্যবস্থা দুর্বল হয়। সাধারণ জনগণ যখন দেখেন প্রশাসনের কেউ সেবা দিচ্ছে না, বরং ঘুষ না দিলে কাজ হয় না, তখন তারা নিজেরা শর্টকাট খুঁজে নিতে বাধ্য হয়। কেউ কেউ অপরাধে জড়িয়ে পড়ে, কেউ আবার আমলাতন্ত্রকে ফাঁকি দেয়ার পথ খুঁজে নেয়।
একজন কৃষক যখন সার বা ঋণের জন্য কৃষি অফিসে যায়, তখন যদি দেখতে পায় দলীয় পরিচয় ছাড়া কোনো সুবিধা মিলছে না, তাহলে তার রাষ্ট্রের ওপর আস্থা থাকে না। আবার একজন শিক্ষার্থী যখন সরকারি চাকরির পরীক্ষায় ভালো করেও দলীয় পরিচয় না থাকায় বাদ পড়ে, তখন সে প্রতিবাদে নয়, প্রতিশোধে উদ্বুদ্ধ হয়। এসব ছোট ছোট অবিচার থেকে জন্ম নেয় বড় অপরাধ, বিদ্বেষ এবং অস্থিরতা। যখন উচ্চপর্যায়ের নেতারা কোটি কোটি টাকার দুর্নীতিতে জড়িত থাকেন, অথবা তাদের পরিবারের সদস্যরা রাতারাতি বেপরোয়া সম্পদের মালিক হন, তখন তা সমাজে এক ভয়াবহ বার্তা পৌঁছে দেয়।
সাধারণ মানুষ, এমনকি আমলারা ও পুলিশ সদস্যরাও ভাবতে শুরু করেন, ‘যদি বড় কর্তাই এভাবে লুটপাট করতে পারেন, তাহলে আমাদের ছোট-খাটো সুযোগ নিলে দোষ কোথায়?’ এই মানসিকতাই ছোট-খাটো দুর্নীতি থেকে শুরু করে বড় অপরাধে জড়িয়ে পড়ার নৈতিক অজুহাত তৈরি করে। ভণ্ড নেতৃত্ব সমাজের নৈতিক কম্পাসকেই বিকৃত করে দেয়।
নেতারা প্রায়শই আইনকে নিজেদের সুবিধামতো ব্যাখ্যা করেন বা সরাসরি অমান্য করেন। তাদের গাড়িবহর ট্রাফিক আইন ভঙ্গ করে, তাদের সমর্থকরা জোর করে জমি দখল করে, তাদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ প্রক্রিয়াগত জটিলতায় আটকে যায়। এই ‘ঊর্ধ্বতন আইনহীনতা’ সমাজের সর্বস্তরে আইনের প্রতি অবজ্ঞা ও ভীতিহীনতা তৈরি করে। যদি নেতারাই আইন ভঙ্গ করতে পারেন, তাহলে সাধারণ মানুষের পক্ষে ছিনতাইকারী বা চোর কেন আইন মানবে?
রাজনীতি, প্রশাসন এবং সমাজের মধ্যে যে নৈতিক বন্ধন থাকা উচিত, তা ছিন্ন হয়ে গেছে। আজ সাধারণ মানুষ পুলিশ দেখলে নিরাপদ নয়, বরং আতঙ্কিত হয়। একজন বৃদ্ধ রিকশাচালক জানেন, তাকে থানায় যেতে হলে ‘বাবুদের’ মিষ্টি খাওয়াতে হবে। সাধারণ মানুষ মনে করেন, অপরাধ করলে শাস্তি পাওয়ার সম্ভাবনা কম, যদি ‘সঠিক লোকের’ আশ্রয়ে থাকা যায়। এই মানসিকতা আমাদের সমাজকে ধীরে ধীরে এক নৈরাজ্যের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। রাজনৈতিক ভণ্ডামি ও আমলাতান্ত্রিক দুর্বৃত্তায়নের ফলে আজ অপরাধীরা বীর, আর সৎ মানুষ উপহাসের পাত্র।
নির্বাচনী মঞ্চে জনগণের দুঃখ-দুর্দশার সমাধানের জ্বালাময়ী প্রতিশ্রুতি, ক্ষমতায় আসার পরই বাতাসে মিলিয়ে যায়। এই ক্রমাগত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ জনগণের মধ্যে হতাশা, ক্ষোভ ও ক্ষমতাহীনতার জন্ম দেয়। এই হতাশাই অনেককে বিকল্প পথে, এমনকি অপরাধের পথেও ঠেলে দিতে পারে। অন্যদিকে, প্রতিশ্রুত সেবা না পেয়ে জনগণকে যখন বারবার অফিসে ঘুরতে হয়, তখন দুর্নীতির সুযোগ তৈরি হয়।
রাজনৈতিক নেতাদের এই ভণ্ডামি ও নৈতিক অধঃপতনের সরাসরি শিকার হয় রাষ্ট্রযন্ত্রের অন্যতম স্তম্ভ- আমলাতন্ত্র। এর ফলাফল ভয়াবহ-
পক্ষপাতদুষ্ট নিয়োগ ও পদোন্নতি: যোগ্যতা ও মেধার ভিত্তিতে নয়, রাজনৈতিক আনুগত্য ও ঘনিষ্ঠতার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ দেয়া হয়। ফলে অযোগ্য, দুর্নীতিগ্রস্ত ও নীতিহীন ব্যক্তিরা ক্ষমতাবান পদে বসে। তারা জনসেবার চেয়ে রাজনৈতিক প্রভুদের সন্তুষ্টি ও ব্যক্তিগত লাভকে প্রাধান্য দেয়।
দুর্নীতির সংস্কৃতি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ: রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় দুর্নীতি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নেয়। ফাইল আটকানো, অহেতুক তদন্ত চাওয়া, জটিল প্রক্রিয়া তৈরি করা- এগুলো দুর্নীতি আদায়ের কৌশলে পরিণত হয়। নাগরিকদের জরুরি সেবা (জমির দলিল, লাইসেন্স, ভর্তুকি, স্বাস্থ্যসেবা) পেতেও অসংখ্য ঘুষ দিতে হয়। এই ‘গতি টাকার’ সংস্কৃতি আমলাতন্ত্রের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করে।
অদক্ষতা ও দায়িত্বজ্ঞানহীনতার প্রসার: রাজনৈতিক বিবেচনায় নিয়োগপ্রাপ্তরা প্রায়ই নিজ দায়িত্বে অনভিজ্ঞ বা আগ্রহহীন। তারা প্রক্রিয়াগত জটিলতা তৈরি করে নিজেদের অদক্ষতা ও দায়িত্ব এড়ানোর চেষ্টা করে। একটি সাধারণ কাজেও একাধিক স্বাক্ষর, কাউন্টার, নোটিং- এসবের নামে ফাইল মাসের পর মাস ঘোরাফেরা করে। এতে জনগণের সময়, অর্থ ও শক্তি ক্ষয় হয়।
জবাবদিহিতার অভাব: রাজনৈতিক প্রভুরা যখন নিজেরাই দুর্নীতিগ্রস্ত বা ভণ্ড, তখন তারা আমলাদের জবাবদিহি করার নৈতিক অধিকার বা রাজনৈতিক সদিচ্ছা হারায়। দুর্নীতি ও অদক্ষতার অভিযোগ তদন্তের নামে আটকে যায় বা প্রভাবশালীদের হস্তক্ষেপে নিষ্পত্তি হয়ে যায়। ফলে আমলারা আরও নির্ভয়ে দুর্নীতি করতে ও সেবা বঞ্চিত করতে থাকে।
প্রশাসনে দক্ষতা ও নিরপেক্ষতা ফিরিয়ে আনা: মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ এবং রাজনৈতিক হস্তক্ষেপমুক্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন। ঘুষ, তদবির ও দলীয় বিবেচনা যেন নিয়োগ বা পদোন্নতিতে প্রভাব না ফেলে, তা কঠোরভাবে নিশ্চিত করতে হবে।
অপরাধীদের রাজনৈতিক ছত্রছায়া বন্ধ করা: যে-ই হোক, অপরাধ করলে শাস্তি পেতে হবে। রাজনৈতিক দলের উচিত নিজেদের মধ্যে থাকা অপরাধীদের চিহ্নিত করে তাদের বিচারের মুখোমুখি করা। রাজনৈতিক পরিচয় কখনো অপরাধের ঢাল হতে পারে না, এই বার্তা রাষ্ট্রের প্রতিটি স্তরে স্পষ্ট করতে হবে।
জনসচেতনতা ও শিক্ষার মাধ্যমে নৈতিকতা জাগানো: সমাজে নৈতিক শিক্ষা ফিরিয়ে আনা প্রয়োজন। গণমাধ্যম, সাহিত্য, নাটক, সিনেমা, সবকিছু যেন মানুষের বিবেক জাগাতে সহায়ক হয়। তরুণ প্রজন্মকে বলা দরকার, অপরাধ নয়, আদর্শই মানুষকে সম্মান এনে দেয়।
আইনের শাসনের কঠোর প্রয়োগ: বিচারব্যবস্থা ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে অবশ্যই রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত হতে হবে। অপরাধী, তার রাজনৈতিক পরিচয় যাই হোক না কেন, দ্রুত বিচার ও কঠোর শাস্তির আওতায় আনতে হবে। বিশেষ করে রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় চলা অপরাধী চক্রগুলোর বিরুদ্ধে বিশেষ অভিযান চালাতে হবে।
সেবার মান নির্ধারণ ও জবাবদিহিতা: প্রতিটি সেবার জন্য স্পষ্ট সময়সীমা, প্রক্রিয়া ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম প্রকাশ করতে হবে। সময়মতো সেবা না দিলে বা ঘুষ দাবি করলে তার বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেয়ার সহজ প্রক্রিয়া (হটলাইন, অনলাইন পোর্টাল) চালু করতে হবে।
ডিজিটালাইজেশন ও স্বচ্ছতা: ভূমি রেকর্ড, লাইসেন্সিং, টেন্ডারিং, ভর্তুকি বিতরণসহ সর্বত্র ই-গভর্নেন্স চালু করতে হবে। অনলাইনে আবেদন, ট্র্যাকিং এবং পেমেন্টের ব্যবস্থা ঘুষের সুযোগ কমাবে ও প্রক্রিয়া গতিশীল করবে। সমস্ত সরকারি চুক্তি, ক্রয় ও বরাদ্দের তথ্য অনলাইনে প্রকাশ করতে হবে।
দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) শক্তিশালীকরণ: দুদককে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপমুক্ত করে কার্যকর ক্ষমতা ও সম্পদ দিতে হবে। উচ্চপদস্থ আমলা ও রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধেও নির্ভয়ে তদন্ত চালানোর সক্ষমতা দিতে হবে।
নাগরিক সচেতনতা ও সক্রিয়তা: নাগরিকদের ঘুষ দেয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। সহজ পথের প্রলোভন এড়িয়ে আইনানুগ প্রক্রিয়ায় লড়াই করার মানসিকতা তৈরি করতে হবে।
মিডিয়া ও সুশীল সমাজের ভূমিকা: গণমাধ্যমকে অবশ্যই নিরপেক্ষ ও নিষ্ঠার সাথে রাজনৈতিক ভণ্ডামি, দুর্নীতি ও অপরাধের সংযোগ তুলে ধরতে হবে। সুশীল সমাজকে নাগরিক অধিকার সচেতনতা, আইনি সহায়তা এবং শাসন ব্যবস্থার ওপর নজরদারি জোরদার করতে হবে। গঠনমূলক পরিবর্তনের পথ কণ্টকাকীর্ণ, কিন্তু একেবারে অদম্য নয়। এর জন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক শ্রেণির আত্মসমালোচনা ও নৈতিক উত্থান, আমলাতন্ত্রের কাঠামোগত সংস্কার এবং সর্বোপরি, একটি সচেতন, সক্রিয় ও দায়িত্ববান নাগরিক সমাজের জাগরণ।
ভবিষ্যৎ প্রজন্মর জন্য একটি নিরাপদ, সুশাসিত ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গড়ার দায়িত্ব আমাদের সবার। অপরাধ একদিনে সৃষ্টি হয় না। ধীরে ধীরে এর প্রতিফলন ঘটে। আর এই বিকৃতি শুরু হয় রাজনৈতিক ভণ্ডামি থেকে, যেখানে সত্য চাপা পড়ে, আদর্শ পরিত্যক্ত হয় এবং স্বার্থ পরিণত হয় ধর্মে। আমাদের এখনই সময়, এই সমাজব্যবস্থাকে হাইজ্যাকের হাত থেকে রক্ষা করার। প্রয়োজন শুধু সাহস, স্বচ্ছ নেতৃত্ব এবং প্রতিজ্ঞাবদ্ধ নাগরিকের সম্মিলিত চেতনা। যদি আমরা সত্যিই বদল চাই, তবে রাজনীতিকে শুদ্ধ করতেই হবে, সেখানেই লুকিয়ে আছে রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ।
লেখক: শিক্ষক ও কলামিস্ট
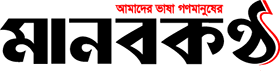





Comments