
আগুন, অতি-পরিচিত একটি শব্দ। দৈনন্দিন জীবনে আমাদের একটি অংশ হিসেবে কাজ করলেও বর্তমানে এই আগুন-ই একটি আতঙ্কের নাম। রান্না-বান্না থেকে শুরু করে প্রায় সবখানেই আমাদের আগুনের প্রয়োজন। এমনকি অতিরিক্ত শীতকে ঠেকাতেও অনেক মানুষ আগুনের শরণাপন্ন হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হচ্ছে, নিত্যপ্রয়োজনীয় আগুন মাঝে মাঝে আমাদের নিঃস্ব করে দেয়। তারপরও আমাদের সতর্কতার ঘাটতি থাকে। আগুনে পুড়ে ছারখার হয়ে যায় দেশের অনেক সম্পদ। প্রতিবছর কোনো না কোনো ঘটনা ঘটে যার রেশ কাটতে না কাটতেই আরেক বড় ঘটনার দাহে আমরা পুরনো শোক কাটিয়ে উঠতে পারি না।
গত ২৯ ফেব্রুয়ারি ঢাকার বেইলি রোডের গ্রীন কোজি নামক একটি বহুতল ভবনে যে অগ্নিসংযোগ হয়, যেখানে জানমালের ক্ষতি হয়। মার্চের এক তারিখের প্রতিবেদন অনুযায়ী ওই অগ্নিকাণ্ডে নিহতের সংখ্যা প্রায় অর্ধশতক। আবার গত ৪ মার্চ চট্টগ্রামের কর্ণফুলী এলাকায় দেশের প্রথম কাতারের ব্যবসায়ী এস. আলম রিফাইন্ড সুগার মিলের গুদামে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। নষ্ট হয়ে যায় রমজানের জন্য রাখা ১ লাখ টন চিনি।
আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছিল ফায়ার সার্ভিসের ১৮টা ইউনিট প্রায় ৭-৮ ঘণ্টা ধরে। তবুও নিয়ন্ত্রণে আনা কঠিন হয়ে গিয়েছিল। হয়তো ভুল পদ্ধতিতে, আগুনের ধরন না বুঝেই অগ্নিনির্বাপণ করার চেষ্টা চালিয়েছিল বা চালায়। তাই হয়তো এত এত ইউনিট কাজ করা সত্ত্বেও আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয় না। বারবার অগ্নিকাণ্ডের পরও তা কেন নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না সে আলোচনা উঠছে সবখানে। বিশেষ করে ঝুঁকিপূর্ণ ভবনগুলো শনাক্ত করার পরও কেন সেগুলোতে বছরের পর বছর ব্যবসা চালিয়ে যায় সে প্রসঙ্গই উঠে আসছে এ আলোচনায়।
পুরান ঢাকার নিমতলী, চকবাজারের চুড়িহাট্টা, আশুলিয়ার তাজরীন গার্মেন্টস, টঙ্গীর ট্যাম্পাকো ফয়েলস প্যাকেজিং কারখানা, বনানীর এফ আর টাওয়ারের পর এবার বেইলি রোড ট্র্যাজেডি অগ্নি দুর্ঘটনার ভয়াবহ সাক্ষী।
ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের বার্ষিক পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, ২০০৪ সাল থেকে ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারি ২০ বছরে বাংলাদেশে প্রায় দুই লাখ ৯ হাজার ৬৮৩টি অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। এসব ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন প্রায় দুই হাজার মানুষ। ২০১০ সালের ৩ জুন পুরান ঢাকার নিমতলীর নবাব কাটারায় ৪৩ নম্বর বাড়িতে রাত ৯টায় রাসায়নিক দাহ্য পদার্থের গুদামে ভয়াবহ বিস্ফোরণে নিহত হন নারী ও শিশুসহ ১২৪ জন।
২০১২ সালে ২৪ নভেম্বর ঢাকা মহানগরীর উপকণ্ঠ আশুলিয়ার নিশ্চিন্তপুর এলাকায় তৈরি পোশাক প্রতিষ্ঠান তাজরীন ফ্যাশনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ১১১ জন নিহত হন। এতে সরাসরি আগুনে দগ্ধ হয়ে মারা যায় ১০১ জন পোশাকশ্রমিক। আগুন থেকে রেহাই পেতে উপর থেকে লাফিয়ে পড়ে মৃত্যু হয় আরও ১০ জনের। ২০১২ সালে গরিব অ্যান্ড গরিব গার্মেন্টসে লাগা আগুনে নিহত হন ২১ জন। এ ছাড়া হামীম গ্রুপের অগ্নিকাণ্ডে ২৯ জনের প্রাণহানি ঘটে। ২০১৩ সালের ২৮ জুন রাজধানীর মোহাম্মদপুরে স্মার্ট এক্সপোর্ট গার্মেন্টস লিমিটেডে আগুনে পুড়ে ৭ নারী পোশাকশ্রমিক নিহত হন।
ট্যাম্পাকো ট্র্যাজেডি: ২০১৬ সালের ১০ সেপ্টেম্বর টঙ্গীর ট্যাম্পাকে ফয়েলস কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ৪১ জন প্রাণ হারান। ২০১৭ সালের ১৫ মার্চ রাত ২টা ৫০ মিনিটে মহাখালীর কড়াইল বস্তিতে আগুনের সূত্রপাত হয়। এর আগে ২০১৬ সালের ০৫ অক্টোবর হাজারীবাগ বেড়িবাঁধ সংলগ্ন শিকদার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পাশে বউবাজার বস্তিতে আগুনে পুড়ে যায় ৫০টি ঘর। ২০১৮ সালের ১৯ নভেম্বর একই বস্তিতে লাগা আগুনে প্রাণ হারান ১১ জন। একই বছর ১২ মার্চ রাজধানীর পল্লবীর ইলিয়াস আলী মোল্লা বস্তিতে আগুন লেগে বস্তির প্রায় ৫ হাজার ঘরের সব পুড়ে যায়। ২০১৯ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি রাত পৌনে ১১টার দিকে রাজধানীর চকবাজারের চুড়িহাট্টায় ওয়াহেদ ম্যানশনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ৭০ জন নিহত হন।
এমন আরো কত শত অগ্নিদাহের ঘটনা আছে তা বলে শেষ করা যাবে না। আক্ষরিক অর্থে বলা যায় গত বিশ বছরে আগুনের ভয়াবহতায় প্রাণ গেছে ২/৩ হাজার মানুষের। কিন্তু তার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত কত পরিবার, কত মানুষ, কত প্রতিষ্ঠান। তারপরও মানুষ সতর্ক হচ্ছে না কেন? এখানে একটা কথা বলা জরুরি। আগুনেরও শ্রেণি বিভাগ আছে। সেগুলো জানা থাকলে আগুন নেভানোর কাজে সুবিধা হয়। আমরা মূলত একধরনের আগুনের সাথে পরিচিত। সেটা হচ্ছে ক্লাস-এ। কিন্তু জ্বালানির উপর নির্ভর করে বিশেষজ্ঞরা আগুনকে ৫ ভাগে ভাগ করে। ১. ক্লাস-এ ২. ক্লাস-বি ৩. ক্লাস-সি ৪. ক্লাস-ডি ৫. ক্লাস-কে। এই পাঁচ ধরনের আগুন নেভাতে পাঁচ ধরনের অগ্নিনির্বাপণ যন্ত্রের দরকার। কিন্তু আমরা সবধরনের আগুন নিয়ন্ত্রণে শুধু পানি ব্যবহার করে থাকি, যা নিতান্তই ভুল। এমনকি সবধরনের আগুনে যদি আমরা পানি ব্যবহার করে থাকি তাহলে ঘটনা বিপরীত হতে পারে।
তাহলে আমরা কোন ধরনের আগুন নেভাতে পানি ব্যবহার করবো? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে যুক্তরাষ্ট্রের দ্য ফায়ার ইকুইপমেন্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশনের দেয়া তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখতে পাই, ক্লাস-এ’ ধরনের আগুন নেভাতে পানি ব্যবহার করতে হবে। কারণ সাধারণত এই ধরনের আগুনের উৎপত্তি কাগজ, কাপড়-চোপড়, কাঠ, বাঁশ, খড় ইত্যাদি সাধারণ পদার্থ থেকে হয়ে থাকে। তাই এ ধরনের আগুন নির্বাপণ করার জন্য পানির ব্যবহার-ই যথেষ্ট। আমরা যখন মাটির চুলায় রান্না করি কাঠ দিয়ে, তখন রান্না হয়ে গেলে সাধারণত আমরা পানি দিয়েই আগুন নিভিয়ে দেই এবং সহজেই আগুন নিভে যায়। তাহলে ‘ক্লাস-বি’ এর আগুন নির্বাপণে আমরা কী বা কোন যন্ত্র ব্যবহার করবো?
মার্কিন দ্য ফায়ার ইকুইপমেন্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশনের তথ্যমতে, যেহেতু এ ধরনের আগুনের সূত্রপাত হয় জ্বালানি তেল, অ্যালকোহল, প্রোপেন গ্যাসের মতো মারাত্মক পদার্থ থেকে, সেহেতু আগুনের তাপমাত্রা থাকে বেশি। এ ধরনের আগুনে যদি পানি ব্যবহার করা হয় তাহলে পানি গন্তব্যে পৌঁছাতে না পৌঁছাতেই বাষ্পে পরিণত হয়ে আগুনের তীব্রতাকে আরো বাড়িয়ে তুলতে পারে। তজ্জন্য পানি ব্যবহার করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এ ধরনের আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য অক্সিজেনের প্রবাহ রুদ্ধ করে দেয় এমন এক্সটিংগুইশারের (অগ্নিনির্বাপণ যন্ত্র) কার্বন-ডাই-অক্সাইড বা রাসায়নিক ফোম ব্যবহার করতে হবে। যেহেতু এ ধরনের আগুন খুব তীব্র হয়ে থাকে সেহেতু আগুন লাগার সাথে সাথে ফায়ার সার্ভিসের সহায়তা নেয়া উচিত।
ক্লাস-সি এর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য কোন জিনিস ব্যবহার করতে হবে? সাধারণত এ ধরনের আগুনের সূত্রপাত হয় বৈদ্যুতিক বা ত্রুটিপূর্ণ ইলেকট্রিক যন্ত্রাংশ থেকে। আমাদের চারপাশে যত্রতত্র বৈদ্যুতিক সংযোগ দেখা যায়। বৈদ্যুতিক সংযোগ দেয়ার সময় যদি ত্রুটিপূর্ণ কোনো কাজ করা হয় তাহলে সাথে সাথেই আগুন ধরে যাবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক স্ট্রাইক ফার্স্টের তথ্যমতে, এ ধরনের আগুন লাগলে প্রথমে বিদ্যুৎ-সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিতে হবে। যদি বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা যায় তাহলে ক্লাস-সি এর আগুন ক্লাস-এ তে পরিণত হয়ে যাবে। ফলে পানির মাধ্যমেও আগুন নেভানো যেতে পারে। যদি বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা না যায় তাহলে কার্বন-ডাই-অক্সাইডযুক্ত অগ্নিনির্বাপণ যন্ত্র ব্যবহার করতে হবে। তখন পানি কিংবা ফোম এক্সটিংগুইশার ব্যবহার করা যাবে না। অন্যথায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হবে না। কারণ ওখানে বিদ্যুৎ পরিবাহী পদার্থ থাকে।
‘ক্লাস-ডি’এর আগুন নির্বাপণে কী করা যেতে পারে? এমন প্রশ্নের জবাব দেয়ার জন্য আগে ক্লাস-ডি এর আগুনের উৎপত্তি সম্পর্কে জানতে হবে। যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব ম্যাসাচুসেটসের এনভায়রনমেন্টাল হেলথ অ্যান্ড সেফটি অফিসের বিশেষজ্ঞদের মতে, বিভিন্ন শিল্পকারখানা মিল ফ্যাক্টেরির পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম ও সোডিয়ামের মতো ক্ষারীয় ধাতু থেকে এ ধরনের আগুনের জন্ম হতে পারে। এসব পদার্থ বায়ু বা পানির সংস্পর্শ পেলে আরো তীব্র হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।
যুক্তরাষ্ট্রের ফায়ার ইকুইপমেন্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশনের মতে, ‘ক্লাস-ডি’ এর আগুন নেভানোর ক্ষেত্রে শুধু ড্রাই পাউডার অগ্নিনির্বাপণ যন্ত্র ব্যবহার করা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কেননা পানি কিংবা ফোম ব্যবহার করলে সোডিয়ামের মতো বিভিন্ন দাহ্য পদার্থ থাকার কারণে আগুন আরো তীব্র হবে।
ক্লাস-কে এর আগুন নেভাতে আমরা কী করতে পারি? যেহেতু ‘ক্লাস-কে’ এর আগুনের উৎপত্তি হয় ভোজ্যতেল বা প্রাণীর চর্বি জাতীয় জিনিস থেকে, সেহেতু পানির ব্যবহার তো কোনোভাবেই করা যাবে না। সাধারণত ‘ক্লাস-কে’ এর আগুন রান্না ঘরে অসাবধানবশত সৃষ্টি হতে পারে। গরম তেলে যেমন একফোঁটা জল পড়লে তেল ছড়িয়ে ছিটিয়ে যায় ঠিক একইভাবে ভোজ্যতেলে আগুন লাগলে পানি ব্যবহার এর ফলে আরো ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাবে আগুন। কেউ কেউ ‘ক্লাস-বি’ এর আগুনের সাথে গুলিয়ে ফেলে ‘ক্লাস-কে এর আগুনকে। কারণ ‘ক্লাস বি’ এর সূত্রপাতও তেল থেকে। নেভানোর ক্ষেত্রে দুটির সামান্য মিল থাকলেও বৈশিষ্ট্যগতভাবে ভিন্ন।
যদি রান্না ঘরে ‘ক্লাস-ডি’ এর আগুন লেগে থাকে তাহলে ভেজা কাপড় দিয়ে আগুন ঢেকে ফেললে আগুন দমন করা যেতে পারে। তবে আগুনের আকার যদি বড় হয়, তাহলে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের ফোম নির্গমনকারী অগ্নিনির্বাপণ যন্ত্রের সাহায্যে আগুন নিভাতে হবে। এ ধরনের যন্ত্র প্রত্যেকটি ঘরে রাখা দরকার নিজেদের আত্মরক্ষার জন্য।
পরিশেষে বলতেই হয় যে, আগুনের কবলে পড়লে বাঁচার কোনো উপায় নেই। বাঁচলেও আধমরা হয়ে বাঁচতে হবে। সেজন্য আগুন থেকে একমাত্র বাঁচার উপায় হতে পারে, সতর্ক থাকা। আগুন নির্বাপণের যন্ত্র প্রত্যেক ঘরে, দোকানে, শপিং মলে থাকা প্রয়োজন। যাতে আগুন লাগার সাথে সাথেই নির্বাপণ করা যায়। কোন ধরনের আগুন প্রথমে তা চিহ্নিত করে সে মোতাবেক যন্ত্রের মাধ্যমে অগ্নি নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে। সহসা, আগুন সবখানে ছড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে ফায়ার সার্ভিসের সহায়তা নিতে হবে।
লেখক: শিক্ষার্থী- ইতিহাস বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।
মানবকণ্ঠ/এফআই
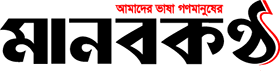





Comments