
মানবজাতির ইতিহাসে বহু গণহত্যার ঘটনা অনেক পুরনো। এমনকি গণহত্যার সংজ্ঞা নিয়েও বিতর্ক বিদ্যমান। গণহত্যার ইংরেজি শব্দ হলো ‘জেনোসাইড’ যার অর্থ হলো ‘কোনো জাতির পরিকল্পিত ধ্বংসসাধন বা ব্যাপক হত্যাকাণ্ড’। গণহত্যা শব্দটি দ্বারা একটি সম্পূর্ণ গোষ্ঠীর জনগণের সর্বনাশ, তাদের অস্তিত্ব থেকে নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা করাকেও বুঝায়। ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ গণহত্যা সংজ্ঞায়িত করেছিল ২নং অনুচ্ছেদে ১৯৪৪ এর আগে এই শব্দটির অস্তিত্ব ছিল না। সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে একটি জাতীয়, নৃতাত্ত্বিক, বর্ণবাদী বা ধর্মীয় গোষ্ঠী ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ক্রিয়াকলাপগুলো গণহত্য হিসেবে বিবেচিত। এর মধ্যে পড়ে পরিকল্পিতভাবে কোনো জাতি বা গোষ্ঠীকে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে তাদের সদস্যদেরকে হত্যা করা। গোষ্ঠীর সদস্যদের গুরুতর শারীরিক বা মানসিক ক্ষতি করা।
সম্প্রতি ড. জিডিয়ন পলিয়া লিখিত একটি গবেষণাধর্মী প্রবন্ধে এক ভিন্নধর্মী গণহত্যার বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতের বঙ্গদেশ অংশে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় দুর্ভিক্ষে ৬০ লাখ লোকের মৃত্যু হয়েছিল। তৎকালীন ব্রিটিশ রাষ্ট্রনায়ক উইনস্টন চার্চিল দুর্ভিক্ষের এই বিপর্যয় থেকে মানুষকে রক্ষা করার দায়িত্ব দৃঢ়তার সঙ্গে অস্বীকার করেছিল। ১৯৪৩-এর এই দুর্ভিক্ষ ৪৩-এর মন্বন্তর হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। চার্চিল ছয় খণ্ডে ‘দ্য সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার’ নামে একটি বিশাল গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এর জন্য তাকে ১৯৫৩ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার দেয়া হয়েছিল। এই গ্রন্থের কোথাও ৪৩-এর মন্বন্তর সম্পর্কে কিছুই উল্লেখ করা হয়নি। অথচ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলেই এই মন্বন্তর হয়েছিল তার মানেই এটা ছিলো গণহত্যা। কিন্তু সেটা কোথাও লেখা হয়নি।
দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধকালে হিটলারের জার্মানিতে যে গণহত্যা সংঘটিত হয়েছে তার একক বৈশিষ্ট্য হলো সুপরিকল্পিতভাবে এবং ঠাণ্ডা মাথায় ধর্মীয়, জাতীয় ও রাজনৈতিক গোষ্ঠীকে নির্মূল করা। নাজি হলোকাস্ট কেন্দ্রিক ট্র্যাজেডি প্রত্যক্ষ করে পোল্যান্ডের আইন বিশেষজ্ঞ রাফায়েল লেমকিন জেনোসাইড শব্দটি চয়ন করেছিলেন। কিন্তু গণহত্যাকে এড়িয়ে যাওয়া বা অস্বীকার করায় ইতিহাসের গতিধারার কোন বদল হয় কি? যদি না হয় তাহলে গণহত্যা অস্বীকারের এই রাজনীতি কি অর্থ বহন করে? বাংলাদেশে ১৯৭১ সালে নয় মাসব্যাপী যে গণহত্যা চালানো হয় তা করেছে পাকিস্তান সামরিক বাহিনী। এই গণহত্যার পরে তাদের লেখা বইগুলো মিথ্যা স্বীকোরোক্তিতে ভরা। সেই কর্মকর্তাদের বিচার করা সম্ভব হয়নি আজও। তারপরও কি ৩০ লাখ মানুষকে হত্যার ইতিহাস মুছে ফেলা যাবে? দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধে হিটলারের ভয়াবহতম হলোকাস্টকে আজও কেউ ভোলেনি। একশ’ বছর পরেও আর্মেনীয় জনগোষ্ঠী প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অটোমান তুর্কিদের গণহত্যার স্বীকৃতির জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরছে।
নেটফ্লিক্সে প্রচারিত ‘দ্য ডেভিল নেক্সট ডোর’ সিরিজে নাজিদের গণহত্যার দয় পোল্যান্ডের ওপর চাপানোর অভিযোগ করেছেন পোল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী। অর্থাৎ এই শতকে এসে অনেকেই গণহত্যার স্বীকৃতি চাচ্ছে,। চাচ্ছে ইতিহাসের ধারাবাহিকতা তুলে ধরতে। কারণ এটি ইতিহাসের দায়। লাঞ্ছনার, নিগ্রহের ইতিহাস মানুষকে সচেতন করে, বোধ শক্তিকে জাগিয়ে তোলে। নতুন প্রজন্ম এই নিগ্রহের ইতিহাস থেকে আগামীর শিক্ষা নেয়। একজন টুপাক আমারোকে তিনশ বছর ভুলে ছিল লাতিন আমেরিকা। স্প্যানিশ আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়েছিলেন বীর টুপাক।
স্প্যানিয়ার্ডরা ফাঁসিতে ঝোলানোর মুহূর্তে টুপাক আমারো মাতা ধরিত্রীকে সাক্ষী রেখে বলেছিলেন, ‘আমি আবার ফিরে আসবো’। টুপাক ফিরে এসেছিল তিনশো বছর পরে, সিমন বলিভারের নেতৃত্বে যখন গোটা লাতিন আমেরিকাজুড়ে তুমুল স্বাধীনতার যুদ্ধ তখন টুপাক আমারোর আত্মদান হয়েছিল তাদের অনুপ্রেরণা। একইভাবে বলা যায় ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ২৫ মার্চ কালরাত্রিতে ‘অপারেশন সার্চলাইট’ নামে ঘুমন্ত বাঙালির উপরে যে গণহত্যা চালিয়েছিলো তা আজও বিশ্বে নজিরবিহীন। ইতিহাসের অবহেলা উপেক্ষার দেবদারু বৃক্ষের মলিনতা নিয়ে দাঁড়ানো আমাদের স্বজনের করোটিতে যারা চাষ করেছিলো হিংসা আর মেতেছিলো খাণ্ডবদাহনে। সেটা মুছে ফেলা সম্ভব?
১৯৭১ সাল। ঢাকা তখন কয়লার অগুনেপোড়া লোহার মতো লাল- বিক্ষুদ্ধ শহর। ঢাকায় স্বাধীনতাকামী মানুষ ততদিনে উড়িয়েছিল স্বাধীনতার পতাকা। এরই মধ্যে ৭ মার্চ তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে শেখ মুজিবুর রহমান ভাষণ দিয়েছেন। তার ভাষণের পরই যেন মানুষ মুক্তির নেশায় বিক্ষুদ্ধ হয়ে উঠেছিল। বাঙালির ইতিহাসের স্বাধীনতা সংগ্রামের ঢেউ কৈবর্ত বিদ্রোহ থেকে তেভাগা, টংক, নানকার ভাওয়ালী বিদ্রোহ হয়ে ভাষা আন্দোলন, শিক্ষা আন্দোলন ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান হয়ে পৌঁছে গিয়েছিলো বাঙালির চেতনার চৌকাঠে। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক বক্তৃতার পর যেন তা তরপায়। বক্তৃতার পরেই ডামি রাইফেল নিয়ে ঢাকার রাস্তায় মার্চ করছেন ছাত্র-ছাত্রীরা। ঢাকায় তখন চলছে মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠক। তাদের গণহত্যারন নীলনক্সা ১৮ মার্চ সমাপ্ত কলে আলোচনার নামে চরছিল কালক্ষেপণ। জুলফিকার আলী ভুট্টোও তখন ঢাকায়। সব মিলে খুবই উত্তেজনাকর পরিস্থিতি। তাদের গণহত্যা চালানোর পেছনের কারণ ছিল কর্তৃত্ব নেয়া। মানে রাজনৈতিক সমঝোতা ‘ব্যর্থ’ হলে সামরিক অভিযান চালিয়ে ‘পাকিস্তান সরকারের কর্তৃত্ব’ প্রতিষ্ঠা করা হবে।
পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতের ওই সেনা অভিযানের সাংকেতিক নাম দিয়েছিল ‘অপারেশন সার্চলাইট’। মেজর জেনারেল খাদিম হুসাইন রাজা তখন পূর্ব পাকিস্তানের ১৪তম ডিভিশনের জিওসি ছিলেন। ‘অপারেশন সার্চলাইট’ নামে সামরিক অভিযানের অন্যতম পরিকল্পনাকারী তিনি। ‘আ স্ট্রেঞ্জার ইন মাই কান্ট্রি ইস্ট পাকিস্তান, ১৯৬৯-১৯৭১’ শিরোনামের একটি স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ তিনি লিখেছেন, ১৯৭১ সালের ১৭ মার্চ রাতে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খান টেলিফোনে মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী এবং মেজর জেনারেল খাদিম হুসাইন রাজাকে কমান্ড হাউজে ডেকে পাঠান। মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী ছিলেন পূর্ব পাকিস্তান গভর্নরের উপদেষ্টা। দুইজন সেখানে যাওয়ার পর টিক্কা খান তাদের বলেন, শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার আলোচনায় ‘প্রত্যাশিত অগ্রগতি’ হচ্ছে না। যে কারণে এখন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ‘মিলিটারি অ্যাকশনে’র জন্য প্রস্তুত থাকতে বলেছেন।
সে অনুযায়ী ১৮ মার্চ সকাল থেকে ক্যান্টনমেন্টে খাদিম হুসাইন রাজার বাসায় রাও ফরমান আলী এবং তিনি দুইজন মিলে অপারেশন সার্চলাইটের খসড়া তৈরি করেন। ঢাকা অঞ্চলে সামরিক অপারেশনের দায়িত্ব নেন রাও ফরমান আলী, আর বাকি পুরো প্রদেশে অভিযানের দায়িত্ব নেন খাদিম হুসাইন রাজা। রাও ফরমান আলী পরিকল্পনায় তার অংশে একটি মুখবন্ধ লেখেন এবং কিভাবে ঢাকায় অপারেশন চালানো হবে তা বিস্তারিত লেখেন। ১৯৭১ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর জনসংযোগ কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন সিদ্দিক সালিক।
‘উইটনেস টু সারেন্ডার’ শিরোনামের একটি বইয়ে তিনি ‘অপারেশন সার্চলাইট’ বিষয়ে লিখেছেন, জেনারেল রাও ফরমান আলী হালকা নীল কাগজের অফিসিয়াল প্যাডের ওপর একটি সাধারণ কাঠ পেন্সিল দিয়ে ওই পরিকল্পনা লিপিবদ্ধ করেছিলেন। সিদ্দিক সালিক লিখেছেন, ‘অপারেশন সার্চলাইট’ নামে পরিকল্পনা ছিল ১৬টি প্যারা সম্বলিত এবং পাঁচ পৃষ্ঠা দীর্ঘ। ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা দেশের বিভিন্ন ব্যারাকে ঘুরে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ব্যবস্থা তদারকি করলেও, অপারেশন সার্চলাইটে অংশ নেয়ার জন্য সামরিক বাহিনীর কারো কাছেই কোনো লিখিত অর্ডার পাঠানো হয়নি। সময় জানিয়ে মেজর জেনারেল খাদিম হুসাইনের কাছে লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খানের কাছ থেকে ফোনটি এসেছিল ২৫ মার্চ সকাল ১১টায়। সংক্ষেপে বলা হয়েছিল, ‘খাদিম, আজ রাতেই।’ সময় নির্দিষ্ট হয়েছিল রাত ১টা। গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারের হিসেবে অবশ্য তখন থাকবে ছাব্বিশে মার্চ। হিসাব করা হয়েছিল, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ততক্ষণে নিরাপদে করাচি পৌঁছে যাবেন। তারপরের ইতিহাস সবার জানা।
ঢাকা শহরেই ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করা হরেয়ছিল ৩০ হাজার মানুষকে। ২৫ মার্চ থেকে শুরু হয় গণহত্যা। ঠাণ্ডা মাথায় তারা ৯ মাসে ৩০ লাখ মানুষকে হত্যা করেছিলো। এত দ্রুত সময়ে এত বড় গণহত্যা বিশ্বের ইতিহাসে ছিলো নজির বিহিন। ঢাকার ইপিআর সদর দপ্তর পিলখানাতে অবস্থানরত ২২তম বালুচ রেজিমেন্টকে পিলখানার বিভিন্ন স্থানে অবস্থান নিতে দেখা যায়। মধ্যরাতে পিলখানা, রাজারবাগ, নীলক্ষেত আক্রমণ করে পাকিস্তানি সেনারা। হানাদার বাহিনী ট্যাঙ্ক ও মর্টারের মাধ্যমে নীলক্ষেতসহ বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা দখল নেয়। সেনাবাহিনীর মেশিনগানের গুলিতে, ট্যাঙ্ক-মর্টারের গোলায় ও আগুনের লেলিহান শিখায় নগরীর রাত হয়ে উঠে বিভীষিকাময়। একাত্তরের পরে বাংলার বাণী, সংবাদ, ইত্তেফাক পত্রিকার পাতায় পাতায় নিখোঁজ সংবাদ। বাংলাদেশের বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে সংঘটিত গণহত্যার সংবাদ, বীরাঙ্গনা, নির্যাতিত মানুষের আত্মত্যাগে সয়লাব ছিল পত্রিকার পাতা। মানুষের মনে সজীব ছিল নির্যাতনের-লাঞ্ছনার ইতিহাস।
পঁচাত্তর পরবর্তী সময়ে মানুষের স্মৃতি থেকে ধীরে ধীরে মলিন হতে শুরু করে নিখোঁজ মানুষের স্মৃতি। মানুষের স্মৃতি থেকে হারাতে শুরু করে হত্যার, লাঞ্ছনার, নিগ্রহের অভিজ্ঞতা। তিন দশকের সামরিক শাসন, স্বাধীনতা বিরোধীদের রাষ্ট্র ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠা মানুষের স্মৃতিকে মুছে দেয়। মানুষ সত্যিই ভুলে যায় একাত্তরের ভয়াবহ নিগ্রহের, লাঞ্ছনার ইতিহাস, বঞ্চনার স্মৃতি। একাত্তর প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে ইতিহাসে বেঁচে থাকবে বিষাদের সুরে, হারানোর শোকে। গণহত্যা ফিরে আসবে যুদ্ধের ইতিহাসে। একাত্তরের যে চেতনা, একাত্তরের যে স্পিরিট- সেটা হারানোর শোক থেকে জন্ম নিয়েছে। লাঞ্ছনার, বঞ্চনার ইতিহাস আমাদের ঘুরে দাঁড়াতে শিখিয়েছে।
আজ সেই গণহত্যার গত পাঁচ দশক পওে নিশ্চয়ই প্রশ্নজাগে আমরা কি ভুলে যেতে চেয়েছি সেই নয় মাসের আতঙ্কিত প্রহর? ৩০ লাখ মানুষের আত্মদানকে? মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ী বীরদের এ সময়ে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় সুবিধা দেয়া হয়েছে। সেটা দেয়া হতেই পারে। বীরদের তালিকা বা তাদের বিভিন্ন সুবিধা দেয়া এটা রাষ্ট্রের কর্তব্য। তাও যে পরিপূর্ণভাবে সঠিক হয়েছে তা বলা যাবে না। তবুও হয়েছে তো। কিন্তু উপেক্ষিত থেকেছে গণশহীদরা, তাদের কোনো তালিকা প্রণয়ন করা হয়নি, দেয়া হয়নি কোনো সুযোগ-সুবিধা। আপাতদৃষ্টিতে এটাকে খুব সাধারণ বিষয় মনে হবে, কিন্তু আসলে এর পেছনে রয়েছে একটা রাজনীতি, যার নাম ‘গণহত্যার রাজনীতি’।
বিশেষত পঁচাত্তর পরবর্তী সামরিক শাসনকালে গণহত্যার সাথে সরাসরি জড়িতরা আবার সক্রিয় হলো রাষ্ট্রে। যে বাঙালি একদিন জীবন বাজি রেখে দেশমাতৃকাকে হায়েনার হাত থেকে শুক্ত করতে জীবনপণ লড়াই করেছে তারা দেশ স্বাধীন করে ঘরে ফিরে গেছে। আর কিছু ফেরেনি। মুক্তির সংগ্রাম কি এত দ্রুত শেষ হয়? হয় না বলেই স্বাধীনতার পরাজিত শক্তির উত্থান আমরা দেখেছি ১৯৭৫ সালের পটপরিবর্তনের পর থেকে। কিভাবে একটা গণবিপ্লব প্রতিবিপ্লবের মাধ্যমে নস্যাত করা হয়েছিল সেটা সবারই জানা। মুক্তিযুদ্ধের পরাজিত শক্তি শাসন ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাদের গাড়িতে উড়েছে ত্রিশ লাখ শহীদের রক্ত ভেজা পতাকা। শুধু কি তাই, বদলে ফেলা হয়েছিলো, দেয়া হলো পাঠ্য বইয়ে জাতীয় ইতিহাস। গণহত্যা, বধ্যভূমি, বীরাঙ্গনাদের বেদনা সব পড়ে রইলো অবহেলা অনাদরে। একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধের বীরগাথা ভয়াবহ গণহত্যা- নির্যাতন কিভাবে বাঙালিরা ভুলে গেল এটা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়।
স্বাধীনতার বিকৃত ইতিহাস পড়ে বেড়ে উঠেছে অনেক প্রজন্ম। যারা বিশ্বাস করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, যুদ্ধাপরাধের বিচার নিয়ে সংশয়ে। এখনো একাত্তরের শহীদের সংখ্যা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। পাকিস্তানি ভাবধারা এদের মগজে এমনভাবে প্রোথিত করা হয়েছে যে এরা বিশ্বাস করে একাত্তরে ভারত নিজেদের স্বার্থে পাকিস্তান ভেঙেছে। মুক্তিযুদ্ধের মৌলিক বিষকে যারা প্রশ্নবিদ্ধ করছে সেই রাজাকার, আলবদর, আলশামসরা আজ শুধু সংগঠিতই না পত্র-পল্লবে বিকশিত। তারা এমন সব মানুষের সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধনে জড়িয়েছে যে তারা প্রতিষ্ঠিত। আমাদের দেশে চালানো পাকিস্তানি হানাদারদের গণহত্যা আজও আন্তর্জাতিকভাবে উপেক্ষিত।
বাংলাদেশকে গত শতাব্দীর অন্যতম ভয়াবহ গণহত্যার শিকার হতে হয়েছে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কর্তৃক সংঘটিত এই গণহত্যাকে অনেকেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ের সবচেয়ে ভয়াবহ গণহত্যা বলে দাবি করেছেন। কিন্তু এই গণহত্যা সম্পর্কে অদ্ভুত নীরবতা লক্ষ্য করা যায়। এই নীরবতা মোটেও রাজনীতি নিরপেক্ষ নয়। তাই এক অস্বীকার করার উপায় নেই। এই নৃশংস গণহত্যাকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির জন্য যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত। এই পদক্ষেপ না নিলে আমাদের ৩০ লাখ শহীদ ও দুই লাখ মা-বোনের আত্মদানের ঘটনার ইতিহাস কালের ধুলায় ঢেকে যাবে। যেটা হবে একটি আত্মঘাতী বিষয়। ইতিহাস সচেতনতা ছাড়া একটি জাতি শিক্ষিত হতে পারে না। সব মাথায় রেখেই জ্বালতে হবে চেতনার আলো, যার মধ্য দিয়ে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তর জানবে বাঙালির বীরত্বের ইতিহাস।
মানবকণ্ঠ/আরএইচটি
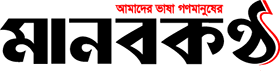





Comments