
বাংলাদেশের রাজনীতিতে এ নির্বাচন এখন অনিশ্চয়তার আরেক নাম। নির্বাচনকালীন সময় ঘোষণার পর সাধারণ মানুষ কিছুটা স্বস্তি পেলেও সেই স্বস্তি বেশিদিন স্থায়ী হচ্ছে না। সম্প্রতি প্রধান উপদেষ্টা ও প্রধান নির্বাচন কমিশনারের ঘোষণা অনুযায়ী ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারির প্রথম ভাগে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে, আর তফসিল প্রকাশিত হবে এ বছরের ডিসেম্বরেই। তবুও দেশের নাগরিকদের মনে সংশয়ের মেঘ কাটছে না। প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে, সত্যিই কি ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে?
সম্প্রতি বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, ‘জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে ষড়যন্ত্রের ডালপালা মেলতে শুরু করেছে। তবে জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক থাকলে কোনো ষড়যন্ত্রই বিএনপির অগ্রযাত্রা থামাতে পারবে না। এ জন্য সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে। গত বছর আমি বলেছিলাম, নির্বাচন ঘিরে অদৃশ্য শক্তি কাজ করছে। আজ তা দৃশ্যমান হয়ে উঠছে। জনগণও তা উপলব্ধি করতে শুরু করেছে।
পতিত, পরাজিত, পলাতক স্বৈরাচারমুক্ত বাংলাদেশে অন্তর্বর্তী সরকার যখন জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার পথে হাঁটছে, তখন কিছু রাজনৈতিক দল নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে নানা শর্ত আরোপ করছে। এতে করে অনেকে ভাবতে শুরু করেছে, নির্বাচনের পথে পরিকল্পিতভাবে বাধা সৃষ্টি করা হচ্ছে।’
নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার পর বিএনপির উচ্ছ্বাস থাকলেও খোদ দলটির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের এ বক্তব্য এখন জনমনে নির্বাচন নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে। অন্য দলগুলো ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান নিয়েছে। জামায়াত নির্বাচন সময় ঘোষণাকে শর্তসাপেক্ষে স্বাগত জানিয়েছে, এনসিপি বলেছে কেবল একটি নির্বাচন নয়, বরং প্রশাসনের নিরপেক্ষতা ও বিচার প্রক্রিয়ার দৃশ্যমান অগ্রগতি নিশ্চিত করতে হবে। ইসলামী আন্দোলন আবার বলেছে, দেশে এখনো নির্বাচনের পরিবেশ তৈরি হয়নি এবং তারা পিআর পদ্ধতির দাবি থেকে সরে আসেনি।
এ থেকে স্পষ্ট, রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের হাতে থাকা কার্ডগুলো এখনো পুরোপুরি খেলেনি। নির্বাচনের দিন যত ঘনিয়ে আসছে, সেই কার্ডগুলো প্রকাশ পাচ্ছে, ফলে অনিশ্চয়তা ও সংশয় আরও ঘনীভূত হচ্ছে। বাংলাদেশের রাজনীতিতে নির্বাচন ঘিরে বিভিন্ন দলের অবস্থান সবসময়ই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। সাম্প্রতিক সময়ে জামায়াতে ইসলামী, ন্যাশনাল কমিটি অব পলিটিক্স (এনসিপি) এবং ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ, এই তিন দলের অবস্থান বিশেষভাবে চোখে পড়ছে।
একদিকে বিএনপি নির্বাচনী উচ্ছ্বাস দেখালেও এই তিনটি দল নানা শর্ত, সংশয় ও আপত্তি তুলে নির্বাচনে অংশগ্রহণ নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে রয়েছে। প্রশ্ন উঠছে, কেন তারা নির্বাচনে যেতে চাইছে না? আর তাদের কৌশলই বা কী? জামায়াতে ইসলামী নির্বাচনের তারিখ ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়েছিল, তবে সঙ্গে সঙ্গে তারা শর্ত জুড়ে দেয়। তাদের বক্তব্য, জুলাই সনদের ভিত্তিতে নির্বাচন হতে হবে এবং সেই সনদকে আইনি ভিত্তি দিয়ে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
অর্থাৎ, তাদের কৌশল হচ্ছে নির্বাচনে অংশগ্রহণের আগে নিজেদের রাজনৈতিক বৈধতা ও সাংগঠনিক স্বীকৃতি নিশ্চিত করা। জামায়াতের নেতাদের দাবি, যদি এই শর্ত পূরণ না হয়, তাহলে নির্বাচনের ফলাফলও গ্রহণযোগ্য হবে না। এনসিপির অবস্থান আরও সতর্ক। তাদের এক নেতা স্পষ্ট বলেছেন, ‘শুধু একটি নির্বাচন করার জন্য গণ-অভ্যুত্থান হয়নি।’ তাদের মূল দাবি হলো নির্বাচনের আগে প্রশাসনের নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা, বিচার ও সংস্কারে দৃশ্যমান অগ্রগতি ঘটানো এবং বর্তমান নির্বাচন কমিশনের পদত্যাগ।
এনসিপি মনে করে, যদি এই কাঠামোগত পরিবর্তন না আনা হয় তবে নির্বাচনে অংশ নেয়া অর্থহীন হবে। তাদের কৌশল তাই চাপ সৃষ্টি করে একটি ‘আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন প্রক্রিয়া’ নিশ্চিত করা। ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের নেতারা আরও সরাসরি নির্বাচনের পরিবেশ অস্বীকার করেছেন। তাদের নেতারা বলেছেন ‘দেশে এখনো নির্বাচনের পরিবেশ তৈরি হয়নি, এ অবস্থায় নির্বাচনে যাওয়া আমাদের পক্ষে কঠিন।’ একই সঙ্গে তারা সংখ্যানুপাতিক (পিআর) পদ্ধতিতে নির্বাচনের দাবি থেকে সরে আসেনি।
অর্থাৎ, তাদের কৌশল হলো নির্বাচনী ব্যবস্থার কাঠামো বদলে নিজেদের জন্য বেশি সুযোগ তৈরি করা। যদি সেই দাবি না মানা হয়, তাহলে তারা নির্বাচনে না গিয়ে সরকারের বৈধতা প্রশ্নবিদ্ধ করার পথে হাঁটবে। অনেকের চোখে এনসিপি, জামায়াত ও ইসলামী আন্দোলন এখন প্রায় একই কাতারের দল। তবে ভেতরে ভেতরে ভিন্নতা স্পষ্ট। এনসিপি ও ইসলামী আন্দোলন প্রকাশ্যে নির্বাচনবিরোধী অবস্থান বজায় রেখেছে, নানা শর্ত না মানা পর্যন্ত তাদের পথে ভোটের মাঠ খোলা নয়।
অন্যদিকে জামায়াত সরাসরি বর্জনের কথা বলছে না, আবার সরলভাবে অংশ নিতেও রাজি নয়। তারা যেন মাঝপথে দাঁড়িয়ে আছে, শর্ত জুড়ে দিয়ে অনিশ্চয়তার আবহ তৈরি করছে। এতে জনমনে নতুন করে সংশয় জন্ম নিচ্ছে, ফেব্রুয়ারি ’২৬-এর ভোট আদৌ কতটা অন্তর্ভুক্তিমূলক হবে। অন্যদিকে বিএনপি এখানে আলাদা জায়গায় দাঁড়িয়ে। তাদের দাবি ছিল দ্রুত নির্বাচন, ডিসেম্বরেই ভোট। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফেব্রুয়ারির সময়সূচি তারা হাসিমুখে মেনে নিয়েছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এর পেছনে রয়েছে হিসাবি কৌশল। বিএনপির বিশ্বাস, যত দ্রুত ভোট হবে, তাদের পক্ষে ফল আসার সম্ভাবনা তত বেশি। দলটির আত্মবিশ্বাস স্পষ্ট, ফেব্রুয়ারির নির্বাচনেই তারা জিতবে। জুলাই সনদ ও সংস্কারপ্রচেষ্টাও দেখায়, নিজেদের ভবিষ্যতের ক্ষমতাসীন শক্তি হিসেবেই তারা ভাবছে। কিন্তু প্রশ্ন থেকেই যায়, বিএনপির জয়ের সম্ভাবনাই কি নির্বাচনকে অনিশ্চিত করার কৌশলকে উসকে দিচ্ছে?
গণ-অভ্যুত্থানের পর নানামুখী শক্তি রাজনীতিতে সক্রিয় হয়েছে। কেউ নৈরাজ্যের পথ ধরে, কেউ আবার বিভ্রান্তি ছড়িয়ে নিজেদের জায়গা খুঁজছে। এদিকে পরাজিত শক্তি আওয়ামী লীগও ভারতে বসে কৌশল সাজাচ্ছে। রাজনীতির জল যত ঘোলা, ততই সুযোগ সন্ধানীদের খেলা জমে উঠছে। অধ্যাপক মুহম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার প্রতিষ্ঠার পর এক বছর অতিক্রান্ত হয়েছে।
দীর্ঘ ১৬ বছরের স্বৈরশাসনের পতন এবং রক্তাক্ত গণ-অভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে এই সরকার দায়িত্ব নিয়েছিল, যা ছিল একই সঙ্গে জনআকাক্সক্ষার প্রতিফলন এবং ইতিহাসের অনিবার্যতা। তবে শুরুর দিন থেকেই তাদের সামনে ছিল নানা জটিলতা: ভেঙে পড়া প্রশাসনকে পুনর্গঠন, আইনের শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা, রাজনৈতিক অস্থিরতা প্রশমিত করা, এবং অর্থনীতিকে ঘুরে দাঁড় করানো। গত এক বছরে অন্তর্বর্তী সরকার কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ নিয়েছে।
প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা, দুর্নীতিবিরোধী পদক্ষেপ, এবং নির্বাচন কমিশনকে নতুন করে সাজানোর উদ্যোগ জনগণের আস্থা বাড়িয়েছে। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি কিছুটা হলেও পুনরুদ্ধার হয়েছে। তবে ব্যর্থতার তালিকাও ছোট নয়। মব জাস্টিক বন্ধে কার্যকরী পদক্ষেপ না নেয়া, নিত্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি, আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় বিচ্ছিন্ন সহিংসতা, এবং বিচার সংস্কারে ধীরগতি নাগরিকদের হতাশ করেছে। সর্বোপরি, রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস এখনো কাটেনি, যা গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রার জন্য বড় অন্তরায়।
এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ঘোষিত ফেব্রুয়ারি ২০২৬-এর নির্বাচন। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান অঙ্গীকার ছিল নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন আয়োজন। সেই প্রতিশ্রুতি পূরণের জন্যই সময়সীমা বেঁধে দেয়া হয়েছে। এখান থেকে সরে আসা মানে শুধু সরকারের ব্যর্থতা নয়, বরং গণ-আকাক্সক্ষার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা।
এখন দায়িত্ব রাজনৈতিক দলগুলোর। তাদের উচিত হবে দলীয় স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে এই নির্বাচনকে জাতীয় স্বার্থ হিসেবে দেখা। নির্বাচনকে অনিশ্চিত করার মানে হবে গণতান্ত্রিক সম্ভাবনাকে ধ্বংস করা, যা শেষ পর্যন্ত সব দলের জন্যই আত্মঘাতী। প্রশ্ন উঠছে: নির্বাচন অনিশ্চিত হলে আসলে কার লাভ? ইতিহাস বলছে, প্রতিবার রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হলে গণতন্ত্রের শত্রুরাই শক্তিশালী হয়েছে, স্বৈরাচার, সুযোগ সন্ধানী গোষ্ঠী কিংবা বিদেশি প্রভাব। সাধারণ মানুষ বা রাজনৈতিক দলগুলোর কোনো প্রকৃত লাভ হয়নি কখনো।
বাংলাদেশ আজ এক ক্রান্তিকালে দাঁড়িয়ে। গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে যে গণতান্ত্রিক প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে, তা পূরণে সবচেয়ে বড় শর্ত হলো একটি সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ, অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন। এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কোনো বিভাজন বা সংশয় সৃষ্টি করা মানে দেশকে আবার অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেয়া। এখন সময় এসেছে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রমাণ করার যে তারা সত্যিই জনগণের প্রতিনিধি।
লেখক: সাহিত্যিক ও গণমাধ্যমকর্মী
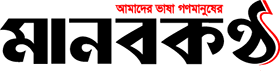





Comments