
গেল ক’বছর আগে আমার এক বন্ধুর সঙ্গে ফরিদপুর গিয়েছিলাম। তিনি নদী গবেষণা কেন্দ্রের একজন সিনিয়র কর্মকর্তা। তার সঙ্গেই নদী গবেষণা কেন্দ্রে আরামদায়ক অতিথিশালায় রাত কাটালাম। শহর থেকে দূরে এই অতিথিশালার বারান্দায় দাঁড়ালাম প্রভাতী প্রকৃতির রূপদর্শনের লোভে। কিন্তু আমার দৃষ্টি থেমে গেল তাদেরই সৃজন করা শিশু আর মেহগনি বনে।
খোঁজ নিয়ে জানলাম, বেশ ক’একর জমিতে এই শিশু আর মেহগনি রোপণ করা হয়েছে। কোনো প্রকার মিশ্র বনায়ন নয়, একক রোপণ। শিশু তো নির্ভেজাল শিশু, এরপর শুধুই মেহগনি। প্রাচীরের এ পাশে নিতান্ত অবহেলায় কটি আম, কাঁঠাল আর দুটি কাঁঠালিচাঁপার চারা রাজবাড়ীর হতদরিদ্র ঝিয়ের মতো লজ্জায় মুখ লুকোচ্ছে। অনেকক্ষণ কান পেতে রইলাম পাখির কলকাকলি শোনার আশায়।
বলা বাহুল্য, কিছুই শ্রবণেন্দ্রিয়ে প্রবেশ করেনি। চোখ মেলে চাইলাম, কোনো পাখি নেই। মনটা বিষণ্নতায় ভরে গেল। হৃদয়ের গভীর থেকে কান্নার ধক্ষনির মতো শুনতে পেলাম আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর উচ্চারণ-
পাখিরা বসতে পারে এমন/ কোনো বৃক্ষ নেই
জোনাকি লুকাতে পারে এমন/ কোনো গুল্ম নেই/ সূর্য শীতল হবে এমন কোনো/ নদী নেই।
বাংলোর অতিথিশালার প্রধান ভবনের সম্মুখে সারি সারি ইউক্যালিপটাস, একাশিয়া (আকাশমণি) শির উঁচু করে দাঁড়িয়ে। শিশু, মেহগনি, একাশিয়া, ইউক্যালিপটাস সুন্দর ফুলে ফুলে আমাদের মুগ্ধ করে না। তারা পাখির আবাস নয়, পাখির খাদ্যও যোগায় না। একাশিয়া, ইউক্যালিপটাস তো ছায়াঘন বৃক্ষও নয়। পৃথিবীর উষ্ণতা রোধে এদের ভূমিকা বরং নেতিবাচক। দারুমূল্যও নেই, জ্বালানি ছাড়া। বেরিয়ে এলাম অতিথিশালার প্রধান ফটক পেরিয়ে রাস্তায়। একটি পুরনো বটগাছ আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানালো।
যানবাহনের তীব্র শব্দ ভেদ কওে কোকিলের কুহুরবে উৎকর্ণ হলাম। চেয়ে দেখি হাজার হাজার লাল ফলে বটগাছটি ভরে আছে। তাতে ভিড় করেছে রাজ্যের পাখি। কোকিল, ঘুঘু, দোয়েল, শালিক থেকে হরেক পাখির কলতানে হারিয়ে গেল যান্ত্রিক বীভৎসতা। একটু দূরে দেখি, গ্রাম ছুঁয়ে অগ্নিলাল কৃষ্ণচূড়ার বন্যা। তাতে স্নিগ্ধতার পরশ বোলাচ্ছে কোথাও বেগুনি জারুল, কোথাও সোনালি সোনালু। আর আছে আম, জাম, জারুল, লিচু, কাঁঠালের মতো নানা ফলবান বৃক্ষ। তৃপ্তিতে মনটা ভরে গেল।
পাশাপাশি দুই বিপরীত দৃশ্য দেখে আমি আমার দেশের উন্নয়নবিদদের স্মরণ করলাম এবং ভয়ে শিউরে উঠলাম। আমার দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানরা আমাদের প্রশাসন আলোকিত করেন। সবচেয়ে মেধাবী সন্তানরা এ দেশে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, প্রশাসক, উন্নয়ন পরিকল্পক হন। তারা আমাদের উন্নয়ন পরিকল্পনা রচয়িতা ও বাস্তবায়নকারী। সেই সবচেয়ে মেধাবী, সবচেয়ে প্রতিশ্রুতিশীল সন্তানদের হাতে আমার দেশের আজ এ হাল কেন? আমি হৃদয়ের গভীরে রক্তক্ষরণ অনুভব করছি। হায় রে আমার সবুজ-শ্যামল বাংলাদেশ! বিকেলে রওয়ানা হলাম পল্লীকবি জসীমউদ্দীনের বাড়ি ও সমাধির উদ্দেশে। অম্বিকাপুরে চলেছি।
হঠাৎ রাস্তার পাশে নর্দমার ওধারে ঝোপের মধ্যে পাশাপাশি পুষ্পভারাবনত দুটি বড়সড় হিজল গাছ। নাকছাবির মতো অপূর্ব লাল দীর্ঘ মঞ্জরিতে আচ্ছন্ন। দেখে প্রাণ জুড়িয়ে গেল। শহরে ফুলে ফুলে ঢাকা পাশাপাশি দুটি হিজল গাছ দেখতে পাব এমন দুরাশা করিনি। ভালো করে চেয়ে দেখি ওই জায়গাটা উন্নয়ন কর্মসীমার বাইরে। কবির সমাধিতে আমার কাঁদতে ইচ্ছে হলো। উন্নয়ন কর্মীদের দীর্ঘ হস্তের নিষ্ঠুর আঘাতে পল্লীকবির নিতান্ত অবহেলিত বাড়ির আঙিনাও ক্ষত-বিক্ষত। বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের হাই ভোল্টেজ লাইনকে বিপন্নক্ত করতে (!) নিষ্ঠুরভাবে ছেদন করা হয়েছে পথপার্শ্বেও সারিবাঁধা নানা বৃক্ষ। আর মুণ্ডিতশীর্ষ বৃক্ষকুল কাতর মুখে প্রতিটি দর্শনার্থীর কাছে নালিশ জানাচ্ছে তাদের ওপর মানুষের নিষ্ঠুর আচরণের কথা।
বাংলাদেশে বৃক্ষরোপণ অভিযান অপ-পরিকল্পনার চূড়ান্ত নিদর্শন। দেশ ছেয়ে গেছে মেহগনি, শিশু, ইপিল-ইপিল আর একাশিয়ায়। এ সবই বিদেশি বৃক্ষ। আমরা বিদেশি তরু রোপণের বিরোধী নই। তবে এসব বিদেশি তরুকে আমাদের পরিবেশে অভিযোজিত হতে সময় দিতে হবে। বিশেষ করে বিবেচনা করতে হবে তাদের সংখ্যানুপাত। তাছাড়া এদের কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া আমাদের পরিবেশে পড়ে কিনা তাও দেখতে হবে। যে কোনো তরুণ ব্যাপক একক রোপণ কতটা বৈজ্ঞানিক তা অবশ্যই পরীক্ষা করে দেখতে হবে।
মূল্যবান কাঠের জন্যই সম্ভবত মেহগনির কদর বেশি। মেহগনির উচ্চ দারুমূল্য নিতান্ত কম নয়। কিন্তু একাশিয়া, ইউক্যালিপটাসের বেলায় তো সে যুক্তিও অচল। তবু এই পরিবেশ বৈরী তরুণ এমন অবাধ একক রোপণ কেন? এর উত্তর আমার জানা নেই। প্রকৃতির ধর্ম বৈচিত্র্য। জীববৈচিত্র্য জীবের অস্তিত্বের প্রধান শর্ত। আমরা সেই প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন করে চলেছি। ইতোমধ্যেই দেশে শিশু গাছে ব্যাপক মড়ক লেগেছে। লাখ লাখ শিশুগাছ দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত। খোদ রাজধানীতে ওসমানী উদ্যান, পান্থকুঞ্জ, চন্দ্রিমা উদ্যান, এয়ারপোর্ট রোডের অনেকখানি জুড়ে আকাশমণির একাধিপত্য।
শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের প্রবেশপথে অনেকগুলো মৃত আকাশমণি আমাদের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিকে ব্যঙ্গ করছে। মেহগনি যে আক্রান্ত হবে না তার নিশ্চয়তা কোথায়? প্রকৃতি তো কারো একচ্ছত্র রাজত্ব বরদাশত করে না। বিশিষ্ট তরু ও পরিবেশবিজ্ঞানীরা মেহগনির হুজুগে রোপণ সম্পর্কে আমাদের সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন; ‘সারা দেশেই এ গাছের (মেহগনি) ঢল। রাজপথ তো বটেই বিদ্যায়তনে, হাসপাতালে, পার্কে সর্বত্রই এ বিদেশি বৃক্ষপ্রজাতির একচ্ছত্র রাজত্ব এবং বলা যায়, আমাদের উন্নয়নের প্রতীকে পরিণত। হুজুগ। আমরা বৈচিত্র্যেও আবশ্যিকতা-বিস্মৃত।
কিন্তু বৃক্ষটি হঠাৎ কোনো মারাত্মক সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হলে কেটে ফেলা ছাড়া অন্যতর কোনো চিকিৎসা থাকবে না তখন বাংলাদেশ বৃক্ষহীন হবে। আমরা কি এ সতর্কবাণী অগ্রাহ্য করে আত্মহনন অব্যাহত রাখব? দেশে বৃক্ষরোপণ সম্পর্কে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের অধীন ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব লোকাল গভর্নমেন্ট প্রকাশিত বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা ম্যানুয়েল আমাকে দিব্যজ্ঞান দান করেছে। দেশের বিশিষ্ট সরকারি তরুপণ্ডিতগণ প্রণীত মোট চতুর্দশ অধ্যায় ও ত্রয়োদশ পরিশিষ্ট সম্বলিত পাঁচ শতাধিক পৃষ্ঠার সচিত্র গ্রন্থটি এক কথায় স্ববিরোধিতার একটি আকরগ্রন্থ হিসাবে মর্যাদা দাবি করতে পারে।
দেশের প্রায় সর্বত্র তারা যেসব বৃক্ষ রোপণের ঢালাও নির্দেশ দিয়েছেন সে তালিকার শীর্ষে আছে মেহগনি, শিশু, ইপিল-ইপিল, আকাশমণি এবং ইউক্যালিপটাস। তবে তা একক না মিশ্র রোপণ হবে তা বলা নেই। তাছাড়া উল্লেখ নেই সংখ্যানুপাতও। এই ম্যানুয়েলে রেললাইনের ধারে ইপিল-ইপিল না লাগানোর পরামর্শ দেয়া আছে, অথচ আমাদের রেললাইনের দু’ধারে জুড়ে এখন সেই ইপিল-ইপিলেরই একাধিপত্য। এই গ্রন্থ প্রণেতাগণ দেশের বস্তিবাসীদের প্রতি খুবই সদয়।
বস্তি এলাকায় তাই ফলদায়ক বৃক্ষ রোপণের পরামর্শ দিয়েছেন তারা। তা বৃক্ষগুলো চিনে নিন: কাঞ্চন, অশোক, সোনালু, টগর, শেফালী, গন্ধরাজ, হাসনাহেনা, শ্যামলতা, স্থলপদ্ম, কবরী, রক্তকবরী! অবাক হচ্ছেন? এসব বৃক্ষ আমাদের বস্তিবাসীদের পুষ্টি সরবরাহ না করুক, নাগরিকদের নান্দনিক ক্ষুধা অন্তত মেটাবে। তাই বা কম কিসে? বন বিভাগেরও নিশ্চয়ই অনুরূপ ম্যানুয়েল আছে।
তা কি এর চেয়ে খুব ভিন্ন কিছু হবে? হলে কি দেশের এই হাল হয়? শুধু বৃক্ষরোপণ বরলেই হবে না। বৃক্ষরোপণে নৈরাজ্য দূর করতে হবে। নান্দনিক, কার্যকর ও পরিবেশসম্মত বৃক্ষরোপণ জরুরি। রক্ষা করতে হবে জীববৈচিত্র্য। ফলদ, বনজ, ভেষজ, বৃক্ষ, তরু, গুল্ম ইত্যাদি স্থানোপযোগী বৃক্ষে ভরিয়ে দিতে হবে আমাদের পরিবেশ। তাহলে আমরা সকলেই বাঁচব। নাকি ভুল বললাম?
লেখক: সাংবাদিক ও কলামিস্ট
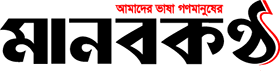





Comments