
বাংলাদেশের স্বাধীনতা-উত্তর রাজনীতিতে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এমন এক চরিত্র, যিনি তার কাজ ও নীতির মাধ্যমে নিজের অবস্থান প্রতিষ্ঠা করেছেন, অথচ নিজেকে প্রচারের জন্য উচ্চস্বরে দাবি করেননি। তার রাজনৈতিক জীবন ও রাষ্ট্রনায়কত্বের ধরন বিশ্লেষণ করলে যে বিষয়টি বিশেষভাবে চোখে পড়ে তা হলো, তিনি ‘কম কথায় বেশি কাজ’ নীতিতে বিশ্বাস করতেন। এই প্রবণতাকে আধুনিক রাজনৈতিক মনোবিজ্ঞানের ভাষায় বলা যায় ‘সিগন্যালিং থিওরি’। এই তত্ত্বের মূল ধারণা হলো, একটি ছোট কিন্তু অর্থবহ সংকেত বা বার্তা মানুষের মনে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলতে পারে, বিশেষ করে যখন সেই সংকেত বাস্তব কর্মের মাধ্যমে সমর্থিত হয়।
জিয়াউর রহমানের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে এই সিগন্যালিং থিওরির প্রয়োগ একেবারেই স্পষ্ট ছিল। তিনি জনসভায় দাঁড়িয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বক্তৃতা দিয়ে জনগণকে আবেগতাড়িত করার চেষ্টায় সময় ব্যয় করেননি। বরং তিনি তার পদক্ষেপের মাধ্যমে বোঝাতে চেয়েছেন, তিনি কী করতে চান এবং কতটা আন্তরিক। এই দৃষ্টিভঙ্গি তাকে অন্যদের থেকে আলাদা করেছে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে যেখানে প্রতিশ্রুতির পাহাড় গড়ে ভোটারদের মন জয় করার চেষ্টা করা হয়, সেখানে জিয়া খুব সংক্ষিপ্ত ভাষণে মূল বিষয় তুলে ধরতেন, কিন্তু সেই বিষয় বাস্তবায়নে সর্বশক্তি নিয়োগ করতেন। তার বিশ্বাস ছিল, কাজই শেষ কথা বলবে, শব্দের জোর নয়।
এই পদ্ধতি কেবল রাজনৈতিক শিষ্টাচারের অংশ ছিল না, বরং এক ধরনের কৌশলগত যোগাযোগ। সামরিক জীবনের কঠোর শৃঙ্খলা ও বাস্তবমুখী সিদ্ধান্ত গ্রহণের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি শিখেছিলেন, অতিরিক্ত শব্দের ভিড়ে বার্তা হারিয়ে যায়। তাই তিনি বেছে নিয়েছিলেন এমন এক ধরনের ভাষা, যা সংক্ষিপ্ত, প্রভাবশালী এবং কর্মের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। মনোবিজ্ঞানের গবেষণায় দেখা গেছে, মানুষ কোনও নেতার দীর্ঘ বক্তৃতার প্রতিটি তথ্য মনে রাখে না; বরং সংক্ষিপ্ত কিন্তু আবেগময় বা যৌক্তিকভাবে শক্তিশালী বার্তা তাদের মনে বেশি স্থায়ী হয়। জিয়া এই মানব-মনস্তত্ত্বকে ভালোভাবেই বুঝতেন।
তার রাজনৈতিক জীবনের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে সিগন্যালিং থিওরির ব্যবহার স্পষ্টভাবে দেখা যায়। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে দেয়া স্বাধীনতার ঘোষণা তার অন্যতম সেরা উদাহরণ। ঘোষণাটি দীর্ঘ বক্তৃতা ছিল না, বরং একটি সরল অথচ শক্তিশালী বার্তা: ‘আমি মেজর জিয়া বলছি- আমি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছি’।
এই সামান্য কয়েকটি বাক্য শুধু সামরিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে নয়, মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকেও অসাধারণ ছিল। কারণ, এটি মুক্তিকামী জনগণকে একটি বৈধতার ছাতার নিচে এনেছিল এবং তাদের মনে আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুলেছিল। রাষ্ট্রপতি হওয়ার পরও তিনি এই কৌশল বজায় রাখেন। বহুদলীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তনের ঘোষণা, গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মসূচির সূচনা কিংবা দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক সহযোগিতার ধারণা, এসব ক্ষেত্রেই তিনি অল্প কথায় মূল বিষয় স্পষ্ট করেছেন।
উদাহরণস্বরূপ, তিনি যখন বহুদলীয় গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার ঘোষণা দেন, তখন সেটি ঘিরে কোনও দীর্ঘ রাজনৈতিক নাটক বা অতিরঞ্জিত প্রচার হয়নি। বরং খুব সোজা ভাষায় তিনি বলেছিলেন, দেশের উন্নয়নের জন্য সবার অংশগ্রহণ দরকার। বার্তাটি ছিল সংক্ষিপ্ত, কিন্তু এর রাজনৈতিক তাৎপর্য ছিল গভীর এবং কার্যকর। সিগন্যালিং থিওরি কেবল জনসভায় ভাষণ দেয়ার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়; এটি নেতার প্রতিটি সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপে প্রতিফলিত হয়। জিয়া তার কর্মসূচি এমনভাবে পরিকল্পনা করতেন, যাতে একটি সিদ্ধান্ত নিজেই জনগণের কাছে বার্তা হয়ে দাঁড়ায়। উদাহরণস্বরূপ, গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মসূচি (জেডিআরএ) চালুর মাধ্যমে তিনি আসলে একটি দ্বিমুখী সংকেত পাঠিয়েছিলেন, প্রথমত, গ্রামই বাংলাদেশের অর্থনীতির মেরুদণ্ড এবং দ্বিতীয়ত, উন্নয়ন তৃণমূল থেকে শুরু করতে হবে।
এই কর্মসূচি চালুর সময় তিনি প্রচুর প্রচার বা আত্মপ্রশংসা করেননি, কিন্তু প্রকল্পের বাস্তব ফলাফলই বার্তাটি বহন করেছিল। মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে, এই ধরনের সংকেত পাঠানোর প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী হয় কারণ এটি বিশ্বাসযোগ্যতার সঙ্গে যুক্ত। কোনও নেতা যদি বড় বড় প্রতিশ্রুতি দেন কিন্তু বাস্তবায়ন না করেন, তবে জনগণ সেই নেতার প্রতি আস্থা হারায়। কিন্তু জিয়া বিপরীত পথে হেঁটেছেন, তিনি সীমিত প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, কিন্তু বাস্তবায়নে সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছেন।
এই পদ্ধতি তার প্রতি আস্থাকে শুধু মজবুতই করেনি, বরং রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যেও একধরনের সতর্কতার পরিবেশ তৈরি করেছিল। এখানে আরেকটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ, সিগন্যালিং থিওরির কার্যকারিতা নির্ভর করে বার্তার ধারাবাহিকতা ও সঙ্গতিপূর্ণতার ওপর। জিয়া তার রাজনৈতিক জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই কৌশল অনুসরণ করেছেন। তিনি হঠাৎ করে কোনও ইমোশনাল বক্তৃতায় জনগণকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেননি। বরং ধীর, স্থিতিশীল এবং ফলাফলমুখী বার্তা প্রদান করেছেন।
এতে জনগণ বুঝতে পেরেছে, এই নেতা হঠকারী নন, বরং পরিকল্পিতভাবে কাজ করেন। এই কৌশল বর্তমান সময়েও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। এখনকার রাজনৈতিক অঙ্গনে যেখানে সোশ্যাল মিডিয়া, টেলিভিশন ও নানা ধরনের প্রচার মাধ্যমের প্রাচুর্য, সেখানে নেতারা প্রায়ই অতিরিক্ত বার্তা পাঠিয়ে জনগণকে ক্লান্ত করে ফেলেন। অথচ জিয়াউর রহমানের উদাহরণ দেখায়, সঠিক সময়ে, সঠিক মাত্রায় এবং সঠিক উপায়ে বার্তা পাঠানোই আসল শক্তি। জনগণকে প্রতিনিয়ত তথ্যের বন্যায় ভাসানোর চেয়ে, মাঝে মাঝে একটি শক্তিশালী সংকেত দেয়া অনেক বেশি কার্যকর। অবশ্য সিগন্যালিং থিওরি প্রয়োগের জন্য কিছু শর্ত পূরণ করতে হয়, যা জিয়া স্বাভাবিকভাবেই করেছিলেন।
প্রথমত, বার্তা হতে হবে বাস্তবতার সঙ্গে মিল রেখে; দ্বিতীয়ত, তা হতে হবে সংক্ষিপ্ত ও প্রভাবশালী; তৃতীয়ত, এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মযজ্ঞ থাকতে হবে। জিয়ার প্রতিটি বড় সিদ্ধান্তের পেছনে কর্মপরিকল্পনা ছিল, যা তার বার্তাকে শুধু শব্দে সীমাবদ্ধ রাখেনি, বরং বাস্তবতার মাটিতে দাঁড় করিয়েছে। তার জীবনের একটি বড় শিক্ষা হলো, নেতৃত্বে বিশ্বাসযোগ্যতা কোনও বিলবোর্ডে কেনা যায় না, এটি তৈরি হয় দীর্ঘমেয়াদি ধারাবাহিক কর্ম ও সঠিক সময়ে সঠিক সংকেত পাঠানোর মাধ্যমে।
জিয়া তার রাজনৈতিক জীবন দিয়ে প্রমাণ করেছেন, জনগণের আস্থা জয়ের জন্য সবসময় উচ্চকণ্ঠ হতে হয় না; বরং নির্ভুল বার্তা ও বাস্তবায়িত কাজই আসল শক্তি। তার প্রয়োগ করা সিগন্যালিং থিওরি শুধু বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে নয়, নেতৃত্ববিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও এক উল্লেখযোগ্য অধ্যয়ন বিষয়।
আজ, যখন আমরা নেতৃত্বের মানদণ্ড নিয়ে প্রশ্ন তুলি, তখন জিয়াউর রহমানের এই যোগাযোগ কৌশল আমাদের নতুন করে ভাবতে শেখায়। তথ্যের প্রাচুর্যের যুগে হয়তো সবচেয়ে বড় নেতৃত্বদক্ষতা হলো, শব্দের ভিড়ে ডুবে না গিয়ে, এমন বার্তা দেয়া যা মানুষের মনে গেঁথে থাকে এবং কর্মের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়। এই পাঠ তিনি রেখে গেছেন আগামী প্রজšে§র জন্য, যা শুধু রাজনীতিতেই নয়, যেকোনো নেতৃত্বের ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য।
লেখক: সাংবাদিক ও কলামিস্ট
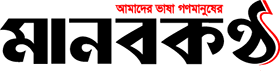





Comments