
বাংলাদেশের সংবিধান আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার ওপর অঙ্গীকারবদ্ধ। বিচারালয়, বিশেষ করে আদালত প্রাঙ্গণ, সেই আইনের শাসনের এক জীবন্ত প্রতীক। এখানে প্রতিটি কার্যক্রমের কেন্দ্রে থাকে ন্যায়বিচার, মানবাধিকার এবং রাষ্ট্রের সার্বভৌম মর্যাদা। কিন্তু সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহ আমাদের সামনে একটি অশনিসংকেত নিয়ে এসেছে। আদালত চত্বরে ডিম নিক্ষেপ, শারীরিক লাঞ্ছনা, অশালীন আচরণ, উসকানিমূলক প্রশ্ন ও ভিডিও ছড়িয়ে দেয়ার মতো নিন্দনীয় ঘটনা যে শুধু ব্যক্তিগত শিষ্টাচারের অভাব প্রকাশ করে তা নয়, বরং এটি আইনের শাসনের ওপর সরাসরি আঘাত হানছে।
এটি সুস্পষ্টভাবে আদালতের অবমাননা এবং বিচারব্যবস্থার প্রতি জনগণের আস্থা নষ্ট করার এক গভীর ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত দেয়। আদালত চত্বর শুধুমাত্র আসামি হাজিরা বা রায় প্রদানের স্থান নয়; এটি একটি পবিত্র স্থান যেখানে ন্যায়বিচারের আশা নিয়ে মানুষ অপেক্ষা করে। এখানকার প্রতিটি কর্মকাণ্ড সংবেদনশীল এবং সুসংহত শৃঙ্খলার অধীন।
আদালত প্রাঙ্গণে অকারণে চিৎকার, হামলা, ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ বা ডিম নিক্ষেপের মতো আচরণ বিচার প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে পারে এবং বিচারকদের ওপর অযাচিত চাপ সৃষ্টি করতে পারে। এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করা মানে বিচারালয়কে ‘পাবলিক ট্রায়াল’-এ নামিয়ে আনা, যেখানে সামাজিক মিডিয়া এবং জনমত দ্বারা বিচারের ধারা নির্ধারণ করা হয় যা একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়।
আইনি দৃষ্টিকোণ স্পষ্ট আইন লঙ্ঘন বাংলাদেশের বিদ্যমান আইন অনুযায়ী আদালত অবমাননা আইন, ১৯২৬ অনুযায়ী, আদালতের প্রতি অবজ্ঞাসূচক কোনো আচরণ শাস্তিযোগ্য অপরাধ। বাংলাদেশ দণ্ডবিধি, ১৮৬০-এর আওতায়, কারো প্রতি প্রকাশ্যে হুমকি, শারীরিক আক্রমণ বা মানহানি করা অপরাধ হিসেবে গণ্য হয়।
ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ অনুযায়ী, ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বা উসকানিমূলক তথ্য প্রকাশ করে জনমনে ভীতি বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করাও শাস্তিযোগ। ডিম ছোড়া বা শারীরিকভাবে আক্রমণ করা শুধু শিষ্টাচার লঙ্ঘন নয়, এটি দণ্ডনীয় অপরাধ। আবার আসামিদের মুখোমুখি উসকানিমূলক প্রশ্ন করে উত্তেজিত করার চেষ্টা এবং সেই প্রতিক্রিয়া সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়ানো এগুলোর মধ্যে স্পষ্টভাবে ‘উসকানি’ এবং ‘আইনি প্রক্রিয়া প্রভাবিত করার’ চেষ্টা নিহিত আছে। বিচারাধীন কোনো আসামির বক্তব্য, অঙ্গভঙ্গি বা প্রতিক্রিয়া ইচ্ছাকৃতভাবে ছড়িয়ে দেয়া জনমনে পক্ষপাতদুষ্ট মনোভাব তৈরি করতে পারে, যা বিচারাধীন বিষয়ের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর।
আমাদের সমাজে বিচারপ্রক্রিয়া নিয়ে উত্তেজনা বা মতভেদ নতুন কিছু নয়। বিচারব্যবস্থার প্রতি সাধারণ মানুষের আশা-আকাক্সক্ষা, অসন্তোষ বা আবেগ এসবই গণতান্ত্রিক সমাজে স্বাভাবিক। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে প্রযুক্তির অপব্যবহার, সামাজিক মাধ্যমে অপপ্রচার এবং বিভ্রান্তিকর ব্যাখ্যার কারণে এই বিচার-উত্তেজনা এক ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে।
সামাজিক মাধ্যমের দ্রুত বিস্তার এই উত্তেজনাকে আরও উস্কে দিচ্ছে এবং ‘ভাইরাল মনস্তত্ত্ব’ নামে এক নতুন ধরনের মানসিক ও সামাজিক প্রবণতার জন্ম দিচ্ছে। বর্তমানে কিছু ব্লগার, ইউটিউবার বা তথাকথিত সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাক্টিভিস্ট বিচারালয়ের মতো সংবেদনশীল স্থানকেও তাদের নাটকীয়তা প্রদর্শনের স্থান হিসেবে বেছে নিচ্ছেন। আদালত চত্বরকে অনেকে যেন ‘লাইভ শো’র মঞ্চ বানিয়ে ফেলেছেন।
মামলার শুনানির দিন আদালতের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে ফেসবুক লাইভ, নাটকীয় সংলাপ, কনফার্মড তথ্য ছাড়াই সন্দেহভাজনের চরিত্র হত্যা এসব যেন রীতিমতো বিনোদনের উপকরণে পরিণত হয়েছে। বিচারাধীন বিষয় নিয়ে জনমত গঠন বা প্রোপাগান্ডা চালানো শুধু নৈতিক বিচারে নয়, আইনগত দিক থেকেও অনভিপ্রেত।
আদালত এখনও রায় দেয়নি, কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ায় অভিযুক্ত ব্যক্তি ইতোমধ্যেই দোষী সাব্যস্ত হয়ে গেছেন। ফলে আদালতের নিরপেক্ষতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়, বিচারপতিরা সামাজিক চাপ অনুভব করেন এবং কখনও কখনও এ চাপে প্রকৃত বিচার বাধাগ্রস্ত হয়। এছাড়া, যারা এই ভাইরাল কনটেন্ট তৈরি করছে, তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আইনি প্রক্রিয়া বা বিচারব্যবস্থার জটিলতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনবগত। অথচ তাদের কথায় প্রভাবিত হচ্ছে লাখো মানুষ, বিশেষ করে তরুণ প্রজন্ম, যারা এসব থেকেই বিচার, ন্যায়বিচার ও নৈতিকতা সম্পর্কে ধারণা নিচ্ছে।
এই পরিস্থিতি যদি চলতেই থাকে এবং কর্তৃপক্ষ কঠোর অবস্থান না নেয়, তবে আমরা এমন এক সমাজে উপনীত হব যেখানে আদালতের জায়গা দখল করে নেবে ফেসবুক কমেন্ট, ইউটিউব থাম্বনেইল এবং ভাইরাল পোস্ট। একদিন বিচারালয়ও সামাজিক চাপ ও জনমতের মুখে নতি স্বীকারে বাধ্য হবে এটি একটি স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক দেশের জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক পরিস্থিতি। এক্ষেত্রে গণমাধ্যমেরও দায়িত্ব রয়েছে, যেন তারা দায়িত্বশীল ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন করে এবং বিচারব্যবস্থাকে সম্মান করে। একইভাবে সমাজের সচেতন নাগরিকদের উচিত বিচারাধীন বিষয়ে সংযত আচরণ করা এবং সোশ্যাল মিডিয়ার অপব্যবহার রোধে ভূমিকা রাখা।
সাম্প্রতিককালে আমরা বিচার ব্যবস্থার উপর জনমতের চাপে দৃষ্টান্তমূলক রায় বা অবমাননার ঘটনাও দেখেছি, যা প্রমাণ করে যে সামাজিক মনস্তত্ত্ব কতটা প্রবল হয়ে উঠছে। এটি শুধু বিচারব্যবস্থার নয়, আমাদের সামগ্রিক সামাজিক নৈতিকতার অবক্ষয়। আদালত চত্বরের শৃঙ্খলা রক্ষা করা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। কোনো মামলার আসামিকে আদালতে হাজির করার পর তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, জনতার ভিড় থেকে দূরে রাখা এবং বিচারপ্রক্রিয়ায় অযথা হস্তক্ষেপ এড়ানো তাদের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে।
কিন্তু বর্তমানে দেখা যাচ্ছে, আদালতের আশপাশে এক ধরনের অরাজক পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে যেখানে আসামিকে ঘিরে হৈচৈ, উত্তেজনা, ছবি তোলা, ভিডিও করা এমনকি লাইভ সম্প্রচারের প্রতিযোগিতা চলছে। এই পরিস্থিতি আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর নিয়ন্ত্রণহীনতা এবং দায়িত্ব পালনের ঘাটতির পরিচায়ক। গণমাধ্যমের নামে কেউ যদি অপরাধীর বক্তব্য প্রচার করে অথবা আদালত চত্বরে নাটকীয়তা তৈরি করে জনতাকে উসকানি দেয়, তাহলে তা কোনোভাবেই সাংবাদিকতার নীতিমালার মধ্যে পড়ে না। বরং এটি বিচারপ্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে এবং আইনের শাসনের প্রতি মানুষের আস্থা নষ্ট করে। এ ধরনের অব্যবস্থার দায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকেই বহন করতে হবে।
তাই আদালত চত্বরে দায়িত্ব পালনরত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর জন্য সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা থাকা জরুরি। পাশাপাশি গণমাধ্যমকর্মীদের জন্যও স্পষ্ট গাইডলাইন তৈরি করা আবশ্যক যাতে তারা শুধু আদালত সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করেন এবং কোনো উসকানিমূলক বা নাটকীয় উপস্থাপনার আশ্রয় না নেন। আদালত চত্বর কোনো ‘সংবাদের বাজার’ নয়, এটি একটি সংবেদনশীল ও সম্মানজনক স্থান যেখানে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর যথাযথ ভূমিকা ও গণমাধ্যমের দায়িত্বশীল আচরণই এই পবিত্র স্থানটির মর্যাদা রক্ষা করতে পারে।
বর্তমান সময়ে বিচারপ্রক্রিয়া নিয়ে সামাজিক উত্তেজনা, গণআচরণের অস্থিরতা ও বিচারব্যবস্থার প্রতি অবিশ্বাস এক ধরনের জাতীয় সংকটের দিকে ইঙ্গিত করছে। প্রযুক্তির অগ্রগতি, সোশ্যাল মিডিয়ার অতিসক্রিয়তা এবং এক শ্রেণির মানুষের অতি আবেগপ্রবণ আচরণ বিচার ব্যবস্থার ওপর এক ধরনের অপছায়া ফেলছে। এই প্রেক্ষাপটে আমাদের সামাজিক ও নাগরিক দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে আমরা যদি আইনের শাসন, আদালতের মর্যাদা এবং বিচারপ্রক্রিয়ার স্বাধীনতা বজায় রাখতে চাই, তাহলে সম্মিলিতভাবে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।
প্রথমত, প্রতিটি নাগরিকের উচিত আইন এবং আদালতের প্রতি সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা। একটি বিচারাধীন মামলার রায় দেয়ার অধিকার একমাত্র আদালতের এটা ভুলে গেলে চলবে না। অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষী কি না, তা বিচারকই নির্ধারণ করবেন, জনসাধারণ নয়। সোশ্যাল মিডিয়ায় অপপ্রচার, আদালতের বাইরে ‘জনগণের আদালত’ বসানো, কিংবা মামলার রায় ঘোষণার আগেই কাউকে ‘অপরাধী’ হিসেবে চিহ্নিত করা শুধুমাত্র ব্যক্তি স্বাধীনতার লঙ্ঘন নয়, বরং আদালতের ওপর এক ধরনের চাপ সৃষ্টির অপচেষ্টা। এই প্রথা বন্ধ না হলে আইনের প্রতি মানুষের আস্থা ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হবে।
দ্বিতীয়ত, গণমাধ্যম ও ডিজিটাল প্লাটফর্ম ব্যবহারকারীদের মধ্যে সংবেদনশীলতা ও দায়িত্ববোধ জাগ্রত করা জরুরি। সাংবাদিকতা স্বাধীন হোক, তবে তা অবশ্যই নৈতিকতার সীমার মধ্যে থাকা উচিত। বিচারাধীন কোনো বিষয় নিয়ে নাটকীয়তা, উত্তেজনা বা প্রভাব বিস্তারের অপচেষ্টা সমাজে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে এবং বিচার প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে। বিশেষ করে কিছু ইউটিউবার, ব্লগার কিংবা সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার আদালত প্রাঙ্গণকে ‘ভিউ’ বা ‘লাইকের’ ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করছেন এটি আদালতের মর্যাদার পরিপন্থী। তাই মিডিয়াকর্মীদের জন্য আদালত সংক্রান্ত রিপোর্টিংয়ে নির্দিষ্ট নীতিমালা থাকা উচিত এবং তা বাস্তবায়নের জন্য কঠোর নজরদারি চালাতে হবে।
তৃতীয়ত, আদালত প্রশাসন এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে আরও কঠোর, দক্ষ এবং দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। আদালত চত্বরে আসামিকে নিরাপদে আনা-নেয়া, অযাচিত জিজ্ঞাসাবাদ, ছবি ও ভিডিও ধারণ নিয়ন্ত্রণ এবং কোনো রকম জনতা উন্মাদনা ঠেকানো আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সাংবিধানিক দায়িত্ব। বিচারাধীন ব্যক্তি আদালতের রায়ের আগ পর্যন্ত কেবল ‘অভিযুক্ত’, আর তাই তার সুরক্ষা নিশ্চিত করা একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রাথমিক কর্তব্য। যদি কেউ আদালত প্রাঙ্গণে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে, বিচার কার্যক্রমকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে বা জনগণের মধ্যে ভুল বার্তা দেয় তাকে দ্রুত আইনের আওতায় আনতে হবে এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।
চতুর্থত, দীর্ঘমেয়াদি সমাধান হিসেবে শিক্ষাক্ষেত্রে আইনি সচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম চালু করতে হবে। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ‘আইনের শাসন’, ‘বিচার ব্যবস্থার স্বাধীনতা’, ‘নাগরিক অধিকার ও দায়িত্ব’, এবং ‘আদালত প্রাঙ্গণের মর্যাদা’ নিয়ে নিয়মিত পাঠ্যক্রম চালু করা যেতে পারে। এতে করে নতুন প্রজন্ম আইনের প্রক্রিয়া, বিচারব্যবস্থার গুরুত্ব ও রাষ্ট্রের কাঠামো সম্পর্কে একটি পরিষ্কার ধারণা লাভ করবে এবং দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠবে।
সবশেষে বলা যায়, বিচারপ্রক্রিয়াকে নিরাপদ, নিরপেক্ষ ও শ্রদ্ধেয় রাখার দায়িত্ব এককভাবে কোনো একটি পক্ষের নয় এটি রাষ্ট্র, মিডিয়া এবং জনগণের সম্মিলিত দায়িত্ব। আমরা যদি সত্যিকার অর্থে ন্যায়ভিত্তিক ও শৃঙ্খলাপূর্ণ সমাজ গঠনে আগ্রহী হই, তাহলে এখনই আমাদের নৈতিকতা, আইনের প্রতি শ্রদ্ধা এবং সামাজিক দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে আসা উচিত। তাহলেই বিচারব্যবস্থা তার প্রকৃত মর্যাদা ফিরে পাবে এবং একটি স্বাধীন ও ন্যায়নিষ্ঠ রাষ্ট্র গড়ে তোলা সম্ভব হবে।
আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সম্মিলিত উদ্যোগ প্রয়োজন। একটি উন্নত, ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র গড়তে হলে আদালত ও বিচারব্যবস্থার প্রতি সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা বজায় রাখা অপরিহার্য। বিচারের আগে অপরাধীকে জনতার আদালতে শাস্তি দেয়া কিংবা সামাজিক মাধ্যমে বিচার বসানো মধ্যযুগীয় বর্বরতার সাথে তুলনীয়। আমরা যদি সত্যিই একটি সভ্য, প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়তে চাই, তবে আদালতের গাম্ভীর্য ও মর্যাদা রক্ষায় আজই আমাদের সবাইকে সচেতন ও দায়িত্বশীল হতে হবে। আসুন, আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার রক্ষায় নিজ নিজ অবস্থান থেকে অবদান রাখি। কারণ আইন ও আদালতের মর্যাদা রক্ষা করা মানেই স্বাধীনতা ও সভ্যতার মশাল বহন করা।
লেখক: গণমাধ্যম কর্মী ও কলাম লেখক
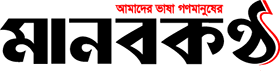





Comments